প্রিয় চাকরিপ্রত্যাশীগণ, আপনাদের জন্য আজকের ব্লগে আমরা ৪৯তম বিশেষ বিসিএস (শিক্ষা) প্রশ্ন সমাধান PDF তুলে ধরছি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার মধ্যে গণ্য হয়। প্রতি বছর লাখ লাখ প্রার্থী এই ধরনের সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।
কেন বিগর সালের প্রশ্ন সমাধান গুরুত্বপূর্ণ?
- প্রশ্নের ধরন বোঝা যায়
- কোন বিষয়ে বেশি প্রস্তুতি দরকার তা চিহ্নিত করা যায়
- কঠিন ও সহজ প্রশ্নের অনুপাত জানা যায়
- ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি পরিকল্পনা সহজ হয়
৪৯তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF-এ থাকছে:
- ৪৯তম বিসিএস প্রিলিমিনারি সম্পূর্ণ প্রশ্ন
- প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা
- গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সসহ সংক্ষিপ্ত নোট
- ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য সাজেশনমূলক বিশ্লেষণ
কারা পড়বেন:
- বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রার্থী
- ব্যাংক, NTRCA বা অন্যান্য সরকারি চাকরি পরীক্ষার প্রার্থী
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন
প্রস্তুতির টিপস:
- শুধু বই পড়া যথেষ্ট নয়; প্রশ্ন অনুশীলন সমান গুরুত্বপূর্ণ
- PDF ডাউনলোড করে নিয়মিত চর্চা করুন
- প্রতিটি প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দুর্বল অংশ চিহ্নিত করুন
- আত্মবিশ্বাসী হয়ে পরীক্ষা দিন
৪৯তম বিসিএস প্রশ্ন সমাধান – জেনারেল পার্ট । 49th BCS Question Solution
৪৯তম বিশেষ বিসিএস (শিক্ষা) প্রশ্ন সমাধান PDF ডাউনলোড । 49th Special BCS Question Solution PD
৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) প্রশ্ন সমাধান – জেনারেল পার্ট
পরীক্ষার তারিখ: ১০ অক্টোবর, ২০২৫
পূর্ণমান: ২০০
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
প্রশ্ন ১. ‘পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু’-এখানে ‘থেকে’ শব্দের সাথে যুক্ত ‘ই’-এর ব্যাকরণিক পরিচয় কী?
ক) উপসর্গ খ) প্রত্যয়
গ) ধাতু ঘ) বলক
সঠিক উত্তর: ঘ) বলক
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: ঘ) বলক।
• বাংলা ব্যাকরণে, শব্দ গঠনের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যেমন উপসর্গ, প্রত্যয়, ধাতু, এবং বলক। প্রশ্নে দেওয়া বাক্য ‘পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু’-এর মধ্যে ‘থেকে’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত ‘ই’ শব্দটির ব্যাকরণিক পরিচয় হলো- বলক।• বলক:
যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালাে হয়, সেগুলােকে বলক বলে।
যেমন –
‘তখনই’ বা ‘এখনও’ পদের ‘ই’ বা ‘ও’ হলাে বলকের উদাহরণ।
অন্য অপশন,
উপসর্গ:
– যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
যেমন-
– অজানা (অ + জানা), অভিযোগ (অভিযােগ), বেতার (বে+তার) প্রভৃতি শব্দের ‘অ’, ‘অভি’, ‘বে’ হলো উপসর্গ।
• প্রত্যয়:
– শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।
যেমন –
→ বাঘ + আ = বাঘা।
→ দিন + ইক = দৈনিক।
উপরের উদাহরণে ‘আ’ ও ‘ইক’ তদ্ধিত প্রত্যয় এবং ‘বাঘা’ ও ‘দৈনিক’ হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ।
ধাতু বা ক্রিয়ামূল:
বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। এসকল ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল।
যেমন: ‘লিখ্ + আ = লিখা; এখানে, লিখ্ হলো ধাতু।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি- নবম ও দশম শ্রেণি (২০২২ সংস্করণ)।
প্রশ্ন ২. আহমদ শরীফের মতে মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে কতজন কবি ছিলেন?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫
সঠিক উত্তর: খ) ৩
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো- খ) ৩
ব্যাখ্যা:
আহমদ শরীফের গবেষণা অনুসারে, মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে তিনজন কবি ছিলেন।
যথা:
১। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস- সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস,
২। চণ্ডীদাস- চৈতন্য পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক এবং
৩। দীন চণ্ডীদাস- আঠারো শতকের শেষার্ধ।
এই তিনজনের রচিত পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী এবং বৈষ্ণব ভক্তির প্রতিফলন ঘটেছে।
• আহমদ শরীফের গবেষণাগ্রন্থ (যেমন: “বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য”) অনুসারে,
উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং আহমদ শরীফের গবেষণাগ্রন্থ (যেমন: “বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য”)।
প্রশ্ন ৩. মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কায়কোবাদ
গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সঠিক উত্তর: গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
ব্যাখ্যা:
মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, যিনি বিশেষত তাঁর ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এবং আধুনিক বাংলা সনেটের জন্য বিখ্যাত। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা করেন। তাঁর পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি কে ছিলেন, তা নির্ধারণ করতে আমাদের সময়কাল এবং সাহিত্যে অবদান বিবেচনা করতে হবে।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১):
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদন দত্তের — পরবর্তী কালের কবি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদনের মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম মধুসূদনের পরে বিকশিত হয়। তাই তিনি মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবি হতে পারেন না।
খ) কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১):
কায়কোবাদ একজন উল্লেখযোগ্য কবি, যিনি তাঁর — ‘মহাশ্মশান কাব্য’ এর জন্য পরিচিত। কিন্তু তিনি মধুসূদনের — পরবর্তী সময়ে সাহিত্যকর্ম শুরু করেন। তাঁর জন্মও মধুসূদনের সক্রিয় সাহিত্যজীবনের পরে। সুতরাং, তিনি পূর্ববর্তী কবি নন।
গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯):
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মধুসূদন দত্তের — পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাংবাদিক। তিনি ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এবং তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জন্য বিখ্যাত। তিনি বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং তাঁর কাজ মধুসূদনের সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তিনি মধুসূদনের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে বিবেচিত হন।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন একজন কবি, সাংবাদিক।
– ‘ভ্রমণকারী বন্ধু’ ছিলো তাঁর ছদ্মনাম।
– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির (মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মিলনকারী) কবি হিসেবে পরিচিত।
– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘সংবাদ প্রভাকর’ সম্পাদনা করেন।
– তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো কবিয়ালদের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা।
– ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও সংবাদ রত্নাবলী, পাষন্ডপীড়ন ও সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।
ঘ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১):
ইসমাইল হোসেন সিরাজী মধুসূদনের — পরবর্তী কালের কবি। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম সাহিত্যের জন্য পরিচিত। তাঁর জন্ম ও সাহিত্যকর্ম মধুসূদনের মৃত্যুর পরে শুরু হয়, তাই তিনি পূর্ববর্তী কবি হতে পারেন না।
তাই বলা চলে, মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ড. সুকুমার সেন), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৪. ‘এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর’- এখানে ‘পরিকর’ শব্দের অর্থ কী?
[মূল প্রশ্নে ‘পরিবার’ লেখা ছিল]
ক) শ্বাস খ) প্রতিজ্ঞা
গ) কোমর ঘ) প্রতিশ্রুত
সঠিক উত্তর: গ) কোমর
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: গ) কোমর।
প্রথমে শব্দের অর্থগুলো জেনে নিই-
• বদ্ধ শব্দের অর্থ- বাঁধা; আবদ্ধ; বাঁধানো।
• পরিকর অর্থ- কটিবন্ধ।
• বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি — “এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর” — এখানে ‘পরিকর’ শব্দের অর্থ কোমর।
‘বদ্ধ পরিকর’ মানে কোমর বেঁধে প্রস্তুত হওয়া বা দৃঢ় সংকল্প করা।
অর্থাৎ বাক্যটির ভাবার্থ —
“এ কাজটি করতে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত।”
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; Accessible Dictionary by Bangla Academy.
সংস্কৃত ‘বদ্ধ’ এবং ‘পরিকর’ শব্দ সহযোগে গঠিত শব্দ হলো বদ্ধপরিকর। এটি বিশেষণ পদ। বদ্ধপরিকর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোর প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সংকল্প, কোনো কাজ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এমন বোঝায় প্রভৃতি। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ‘বদ্ধ’ শব্দের অর্থ হলো, ‘বাঁধা’ আর ‘পরিকর’ শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো, কোমর বা কটিবন্ধ, কোমরবন্ধনী। ইংরেজিতে যেটিকে আমরা বলি বেল্ট। সেই হিসেবে বদ্ধপরিকর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হয় কোমর বা কটিবন্ধ বাঁধা। সংস্কৃত থেকে জাত কোমরবন্ধনী বাঁধা প্রসঙ্গটিই কালক্রমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্থরূপে পরিগ্রহ করেছে।
সূত্র: ‘আজকের পত্রিকা’র রিপোর্ট – “শব্দের আড়ালে গল্প: বদ্ধপরিকর”, লেখক: রাজীব কুমার সাহা, আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক।
অতিরিক্ত আলোচনা:
এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের জন্য আমরা বিগত ৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটি প্রশ্ন যদি পর্যালোচনা করি।
‘গড্ডালিকা প্রবাহ’ বাগ্ধারায় ‘গড্ডল’ শব্দের অর্থ কী?
ক) গরু খ) ছাগল
গ) ভেড়া ঘ) মহিষ
• ‘গড্ডলিকা প্রবাহ’ বাগ্ধারার অর্থ – অন্ধভাবে অনুসরণ। কিন্তু এখানে আক্ষরিক অর্থে ‘গড্ডল’ শব্দের অর্থ ‘ভেড়া’ হয়েছে।
একইভাবে, এখানেও ‘এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর’- বাক্যে পরিকর শব্দের আক্ষরিক অর্থ ধরলে সেটার অর্থ হয় কটি বা কোমর।
প্রশ্ন ৫. ‘শিক্ষককে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী কী চায়’- এই বাক্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োগ হয়েছে-
ক) একবচন বোঝাতে
খ) বহুবচন বোঝাতে
গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে
ঘ) প্রথমটি একবচন, পরেরটি বহুবচন বোঝাতে
সঠিক উত্তর: গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে, ‘শিক্ষক’ এবং ‘শিক্ষার্থী’ শব্দ দুটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ এবং বচন-নিরপেক্ষ (singular and plural neutral) শব্দ, যা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে একবচন (singular) বা বহুবচন (plural) উভয়ই বোঝাতে পারে।
বাক্যটি বিশ্লেষণ করা যাক:
বাক্য: “শিক্ষককে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী কী চায়। ”এখানে ‘শিক্ষক’ এবং ‘শিক্ষার্থী’ শব্দ দুটির সঙ্গে কোনো বচন নির্দেশক শব্দ (যেমন: ‘একজন’, ‘সকল’, ‘অনেক’) যুক্ত নেই। ফলে এগুলো প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে একজন শিক্ষক বা একাধিক শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থী বা একাধিক শিক্ষার্থী উভয়কেই বোঝাতে পারে।
‘শিক্ষককে’ এবং ‘শিক্ষার্থী’ শব্দের বিভক্তি (‘-কে’ এবং বিভক্তিহীন রূপ) কোনো নির্দিষ্ট বচন নির্দেশ করে না। বাংলায় এই ধরনের শব্দ সাধারণত একবচন এবং বহুবচন উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে।
তাই বালা যায়, ‘শিক্ষক’ এবং ‘শিক্ষার্থী’ শব্দ দুটির প্রয়োগ একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ৬. ‘তিনি কথা শুনে ঘুমাতে পারলেন না’ – বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কী হবে?
ক) তিনি কথা না শুনে ঘুমাতে পারলেন না
খ) তিনি কথা না শুনে ঘুমাতে পারলেন
গ) তিনি জেগে রইলেন কথা না শুনে
ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন
সঠিক উত্তর: ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন।
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি — “তিনি কথা শুনে ঘুমাতে পারলেন না” — এটি একটি নেতিবাচক (Negative) বাক্য।
এর অস্তিবাচক (Affirmative) রূপ করতে হলে “না” বাদ দিয়ে অর্থ বজায় রেখে ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করতে হয়।
এখানে,
“ঘুমাতে পারলেন না” = “জেগে রইলেন” (অর্থ একই থাকে)।
অতএব, অস্তিবাচক রূপ হবে —
“তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন।”
অন্যদিকে,
অন্যান্য অপশনগুলোতে নেতিবাচক ‘না’ শব্দটি রয়েছে; যা নেতিবাচক বাক্যের উদাহরণ।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ৭. কোন্ ধ্বনি পরিবর্তনটি যথাযথ নয়?
ক) ক্রন্দন > কাঁদা খ) অঞ্চল > আঁচল
গ) সংগীত > গীতিকা ঘ) দন্ত > দাঁত
সঠিক উত্তর: গ) সংগীত > গীতিকা
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: গ) সংগীত > গীতিকা।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দের রূপান্তর ঘটে, যা প্রায়শই তৎসম, তদ্ভব বা দেশি শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে রূপান্তরের সময় ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, যেমন স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন।
চলুন অপশন বিশ্লেষণ করি —
ক) ক্রন্দন → কাঁদা:
এটি ধ্বনি-পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত। তৎসম শব্দ ‘ক্রন্দন’ (অর্থ: কান্না) থেকে তদ্ভব শব্দ ‘কাঁদা’ (ক্রিয়া, অর্থ: কাঁদা বা কান্না করা) গঠিত হয়েছে।
খ) অঞ্চল → আঁচল:
এটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ। তৎসম শব্দ ‘অঞ্চল’ (অর্থ: কাপড়ের প্রান্ত বা অঞ্চল) থেকে তদ্ভব শব্দ ‘আঁচল’ (অর্থ: শাড়ির প্রান্ত) গঠিত হয়েছে।
গ) সংগীত → গীতিকা:
‘সংগীত’ থেকে ‘গীতিকা’ গঠনের জন্য কোনো সরাসরি ধ্বনিগত পরিবর্তন নেই। বরং এটি অন্য একটি শব্দগঠন (প্রত্যয়যুক্ত রূপ)। ‘গীতিকা’ একটি তৎসম শব্দ, যা ‘গীত’ (গান) শব্দের সঙ্গে ‘-ইকা’ প্রত্যয় যোগ করে গঠিত। ‘গীতিকা’ সংগীতের একটি রূপ বা ছোট গান বোঝায়, কিন্তু ‘সংগীত’ থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি উৎপন্ন হয় না।
ঘ) দন্ত → দাঁত:
এটি স্পষ্ট ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ (স্বরবিকৃতি ও উচ্চারণগত পরিবর্তন)। তৎসম শব্দ ‘দন্ত’ (অর্থ: দাঁত) থেকে তদ্ভব শব্দ ‘দাঁত’ গঠিত হয়েছে।
অতএব, যথাযথ নয় — গ) সংগীত > গীতিকা।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ৮. কাজী নজরুল ইসলামের কোন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাঙ্গীর-
ক) বাঁধন-হারা খ) মৃত্যুক্ষুধা
গ) কুহেলিকা ঘ) শিউলিমালা
সঠিক উত্তর: গ) কুহেলিকা
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ (প্রকাশকাল: ১৯৩১ খ্রি.)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো — জাহাঙ্গীর।
এই উপন্যাসে তিনি একজন শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী চরিত্র — যিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্ধকার দূর করে আলোর পথ খুঁজছেন।
• ‘কুহেলিকা’ উপন্যাস সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ‘নওরোজ’ পত্রিকায় ‘কুহেলিকা’ উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)।
– এ উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে অত্যন্ত বড় ক্যানভাসে।
– উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী স্বদেশি দলের সঙ্গে যুক্ত।
– কিন্তু তার যে প্রেমের সম্পর্ক ও নারী সম্পর্কে ধারণা তা যথেষ্ট ঋণাত্মক।
এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলো হচ্ছে:
– কুহেলিকা,
– তাহমিনা,
– চম্পা,
– ফিরদৌস বেগম।
– নারী সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে:
‘ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু।’
কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য:
– বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
– তিনি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– তাঁর ডাক নাম ছিলো ‘দুখু মিয়া’।
– বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে ‘বুলবুল’ নামে খ্যাত।
• কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস:
– বাঁধন-হারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।
উৎস:
১) বাংলা ভাষা সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
২) বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৯. ‘উৎক্ষেপণ’ শব্দের ‘উৎ’ উপসর্গ কোন্ অর্থ ধারণ করছে?
ক) জোর খ) ঊর্ধ্ব
গ) আড়াল ঘ) গতি
সঠিক উত্তর: খ) ঊর্ধ্ব
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: খ) ঊর্ধ্ব।
ব্যাখ্যা:
‘উৎক্ষেপণ’ শব্দটি গঠিত হয়েছে —
উৎ (উপসর্গ) + ক্ষেপণ (মূল শব্দ)
এখানে ‘উৎ’ উপসর্গের অর্থ হলো ঊর্ধ্ব বা উপরের দিকে।
অর্থাৎ, উৎক্ষেপণ মানে হচ্ছে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা বা উচ্চে ছোড়া।
যেমন: রকেটের উৎক্ষেপণ (রকেটকে আকাশে ঊর্ধ্বে পাঠানো)।
উল্লেখ্য,
– ’উৎ’ একটি তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ।
’উৎ’ উপসর্গটি অন্য যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়-
• ’ঊর্ধ্বমুখিতা” অর্থে- উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন।
• ’আতিশয্য’ অর্থে- উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন।
• ’প্রস্তুতি’ অর্থে- উৎপাদন, উচ্চারণ।
• ’অপকর্ষ’ অর্থে- উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট।
উৎস: ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ এবং মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।
প্রশ্ন ১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দের শুরুতে মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহার করতেন কেন?
ক) এ-কার মাত্রা যুক্ত বলে খ) ‘এ’ মাত্রাহীন বর্ণ বলে
গ) ‘এ’ উচ্চারণ বোঝাতে ঘ) ‘অ্যা’ উচ্চারণ বোঝাতে
সঠিক উত্তর: ঘ) ‘অ্যা’ উচ্চারণ বোঝাতে
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: ঘ) ‘অ্যা’ উচ্চারণ বোঝাতে।
• ‘এ’ এবং ‘অ্যা’ – এর উচ্চারণ:
‘এ’- কারের উচ্চারণ ভিন্নতা (‘এ’ এবং ‘অ্যা’) নির্দেশকল্পে রবীন্দ্রনাথ ‘এ’-কারের মুদ্রণে মাত্রাযুক্ত ও মাত্রাহীন ব্যবহার প্রচলন করেন; যা নির্দেশ করে ধ্বনির পার্থক্য—‘এ’ এবং ‘অ্যা’। শব্দের শুরুতে মাত্রাহীন ‘এ’-কার থাকলে উচ্চারণ সংবৃত হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে ‘এ’ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘মেলা’ শব্দটি যদি মাত্রাহীন ‘এ’-কার দিয়ে লেখা হয়, তার উচ্চারণ হবে স্বাভাবিক ‘মেলা’, যা ‘গেলা’ শব্দের ‘এ’ ধ্বনির অনুরূপ। এ ধরনের উচ্চারণের আরও উদাহরণ হলো: দেবী, সেরা, সেই, বেদনা, মেয়ে, গেলা, জেলা ইত্যাদি।
অপরদিকে, শব্দের আদিতে মাত্রাযুক্ত ‘এ’-কার থাকলে উচ্চারণ বিবৃত হয়, অর্থাৎ ‘অ্যা’ ধ্বনি প্রকাশ পায়। যেমন, ‘মেলা’-র উচ্চারণ হবে ‘ম্যালা’, যা ‘ঠেলা’ শব্দের ‘এ’ ধ্বনির অনুরূপ। তদ্রূপ, কেমন, যেমন, যেন, ফেনা প্রভৃতি শব্দেও এই ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
উৎস: ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১১. কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত?
ক) ডাক্তারখানা খ) হাসপাতাল
গ) আকাশছোঁয়া ঘ) গুণমান
সঠিক উত্তর: ক) ডাক্তারখানা
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ডাক্তারখানা – শব্দটি বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে, প্রত্যয় হলো এমন শব্দাংশ যা কোনো শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে বা শব্দের অর্থ বা ভাব পরিবর্তন করে।
প্রশ্নে দেওয়া অপশনগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:
ক) ডাক্তারখানা:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত। ‘ডাক্তার’ শব্দটির সঙ্গে ‘-খানা’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘ডাক্তারখানা’ গঠিত হয়েছে। ‘খানা’ একটি প্রত্যয়, যা স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে ‘ডাক্তারখানা’ মানে ডাক্তারের চিকিৎসার স্থান বা হাসপাতাল। এটি স্পষ্টভাবে প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ।
খ) হাসপাতাল:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়। ‘হাসপাতাল’ ইংরেজি hospital শব্দ থেকে এসেছে। এটি একটি সম্পূর্ণ শব্দ, যার কোনো অংশ বাংলায় প্রত্যয় হিসেবে যুক্ত হয়নি। এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়।
গ) আকাশছোঁয়া:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়। ‘আকাশছোঁয়া’ একটি সমাসবদ্ধ শব্দ এটি সমাসের মাধ্যমে গঠিত, প্রত্যয়ের মাধ্যমে নয়।
ঘ) গুণমান: এটি সঠিক শব্দ নয়। এর শুদ্ধ শব্দ হবে ‘গুণবান’।
তাই, ডাক্তারখানা শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ১২. ‘সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিরাই চায়না।’- এখানে ভুল ঘটেছে-
ক) বানান ও প্রত্যয়ের খ) অর্থ ও বচনের
গ) অর্থ ও প্রত্যয়ের ঘ) বানান ও বচনের
সঠিক উত্তর: ঘ) বানান ও বচনের
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: ঘ) বানান ও বচনের।
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি হলো: “সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিরাই চায়না।” এই বাক্যে দুটি প্রধান ভুল রয়েছে: বানান এবং বচন (number) সংক্রান্ত।
বানানের ভুল:
বাক্যে “চায়না” লেখা হয়েছে, যা ভুল। বাংলা বানানের প্রমিত রূপে সঠিক শব্দটি হলো “চায় না”।
“চায়না” একটি অপ্রমিত রূপ, যা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হলেও আনুষ্ঠানিক লেখায় গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াপদ ‘চাওয়া’ এর নেতিবাচক রূপে ‘চায় না’ লেখা হয়। উদাহরণ: “সে যেতে চায় না।”
বচনের ভুল:
বাক্যে “অনেক ব্যক্তিরাই” ব্যবহৃত হয়েছে, যা বচনের দিক থেকে ভুল।
“অনেক” শব্দটি ইতিমধ্যে বহুবচন বোঝায়। তাই আবার “রা” (বহুবচন চিহ্ন) যোগ করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে “ই” (বলক) যোগ করলে হবে: অনেক ব্যক্তিই। অথবা “অনেক” ছাড়া হবে: ব্যক্তিরাই।
বাক্যটির সঠিক রূপ হবে: “সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিই চায় না।”
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ১৩. পরিভাষিক শব্দ বলতে বুঝায়-
ক) ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর
খ) বিদেশি শব্দের অনুবাদ
গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ
ঘ) ব্যবহারিক প্রয়োজনে নবনির্মিত শব্দ
সঠিক উত্তর: গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।
ব্যাখ্যা:
পরিভাষিক শব্দ বলতে এমন শব্দ বোঝায় যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়, পেশা, শাস্ত্র, বা ক্ষেত্রের (যেমন: বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। এই শব্দগুলো সাধারণত একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় এবং তাদের অর্থ সাধারণ ব্যবহারের থেকে আলাদা বা সীমিত হতে পারে। উদাহরণ: ‘পরিবাহক’ (conductor, বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রেক্ষাপটে), ‘শিক্ষাতত্ত্ব’ (pedagogy, শিক্ষাবিজ্ঞানে)।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর: ভুল।
পরিভাষিক শব্দ শুধু ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর নয়। এটি যেকোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে এবং তৎসম, তদ্ভব, বা নতুন গঠিত শব্দ হতে পারে। উদাহরণ: ‘অণুজীব’ (microbe) ইংরেজি থেকে এলেও, এটি বিজ্ঞানের পরিভাষা হিসেবে সুনির্দিষ্ট।
খ) বিদেশি শব্দের অনুবাদ: ভুল।
পরিভাষিক শব্দ বিদেশি শব্দের অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো স্থানীয়ভাবে গঠিত বা বিষয়ভিত্তিক শব্দও হতে পারে। উদাহরণ: ‘গ্রন্থাগার’ (library) বিদেশি শব্দের অনুবাদ, কিন্তু পরিভাষা হিসেবে এটি গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট।
ঘ) ব্যবহারিক প্রয়োজনে নবনির্মিত শব্দ: আংশিকভাবে সঠিক, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়।
কিছু পরিভাষিক শব্দ নতুন করে গঠিত হতে পারে (যেমন: ‘দূরদর্শন’ বা ‘টেলিভিশন’), কিন্তু সব পরিভাষিক শব্দ নবনির্মিত নয়। অনেক পরিভাষা তৎসম বা প্রচলিত শব্দ থেকেও আসে (যেমন: ‘শিক্ষাতত্ত্ব’ বা ‘অর্থনীতি’।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১৪. ‘মৃগয়া’ শব্দের মৃগ বলতে কি বোঝানো হয়?
ক) বানর খ) সিংহ
গ) পশু ঘ) বন
সঠিক উত্তর: গ) পশু
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ‘মৃগয়া’ শব্দের ‘মৃগ’ বলতে ‘পশু’ বোঝানো হয়।
• উল্লেখ্য,
‘মৃগ’ শব্দের অর্থ – হরিণ, পশু।
‘মৃগয়া’ শব্দের অর্থ – হরিণ শিকার; বন্য পশুপাখি শিকার।
অন্যদিকে,
• ‘বানর’ শব্দের অর্থ – বাঁদরসুলভ স্বভাববিশিষ্ট, শাখামৃগ, মর্ব।
• ‘সিংহ’ শব্দের অর্থ – মৃগেন্দ্র, স্ত্রী. সিংহী /শিংহি।
• ‘বন’ শব্দের অর্থ – অরণ্য, জঙ্গল, কানন, কুঞ্জ, গহন, বিপিন।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।
প্রশ্ন ১৫. কোন শব্দটি বিসর্গসন্ধির মাধ্যমে গঠিত?
ক) নীরব খ) উজ্জ্বল
গ) মানোত্তীর্ণ ঘ) সংগ্রাম
সঠিক উত্তর: ক) নীরব
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• বিসর্গসন্ধির মাধ্যমে গঠিত শব্দটি হলো – নীরব।
শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ, নিঃ + রব = নীরব।
অন্যদিকে,
– ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে = ব্যঞ্জনসন্ধি – আগে ৎ বা দ্ এবং পরে চ্ বা ছ্ থাকলে ৎ বা দ্ স্থানে চ হয়। এবং ৎ বা দ্ -এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকলে ত্ দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন – উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
– ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে = ব্যঞ্জনসন্ধি – ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার হয়। যেমন- সম্ + সার = সংসার, সম্ + গ্রাম = সংগ্রাম।
– প্রথম পদের শেষের অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথম হ্রস্ব-উ ধ্বনি বা দীর্ঘ-উ ধ্বনির যোগে ও-ধ্বনি হয়। বানানে তা ও-কারের রূপ নিয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন: কাল + উত্তীর্ণ = কালোত্তীর্ণ, মান + উত্তীর্ণ = মানোত্তীর্ণ।
বিসর্গ সন্ধি:
– পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদের প্রথমে চ্ বা ছ্ থাকলে বিসর্গ পরিবর্তিত হয়ে শ্, ট্ বা ঠ্ থাকলে ষ্; ত থাকলে স্ হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনে তা যুক্ত হয়।
যেমন:
– নিঃ + চয় = নিশ্চয়,
– দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা,
– নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র,
– শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯-সংস্করণ)।
প্রশ্ন ১৬. ভাষার অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
ক) অক্ষর খ) রূপমূল
গ) শব্দ ঘ) বর্গ
সঠিক উত্তর: খ) রূপমূল
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: খ) রূপমূল।
• শব্দ ও রূপমূল:
শব্দকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করলে এমন উপাদান পাওয়া যায় যা অর্থ প্রকাশে অংশগ্রহণ করে। ভাষার এই ক্ষুদ্রতম অর্থযুক্ত একককে বলা হয় রূপমূল। অর্থাৎ, রূপমূল হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান যাদের সুস্পষ্ট অর্থ থাকবে বা অন্ততপক্ষে অর্থের কোনো যৌক্তিক ইঙ্গিত থাকবে।
আমরা জানি, ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনিমূল, তবে ধ্বনিমূলের মধ্যে কোনো অর্থ বহন করার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে, রূপমূল সর্বদা কোনো না কোনোভাবে অর্থসংশ্লিষ্ট থাকে।
উদাহরণ:
• শব্দ: অবোধ।
• রূপমূল বিশ্লেষণ: অ + বোধ,
এখানে,
• ‘অ’ → উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত, স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে না পারলেও অভাব বোঝায়।
• ‘বোধ’ → স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
রূপমূলের শ্রেণীবিন্যাস:
– মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme): স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
উদাহরণ: বোধ, গান, মাটি।
– বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme): স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ বোঝায়।
উদাহরণ: ‘অ’ (অবোধে), ‘উৎ’ (উৎক্ষেপণে)।
উৎস: উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
প্রশ্ন ১৭. ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য কোথায়?
ক) লেখার ধরনে খ) উচ্চারনের বিশিষ্টতায়
গ) সংখ্যাগত পরিমানে ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে
সঠিক উত্তর: ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনি এবং বর্ণ দুটি ভিন্ন ধারণা, এবং এদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত তাদের প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে নিহিত। নিচে এই পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো:
ধ্বনি:
ধ্বনি হলো মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ বা কথনের একক, যা কান দিয়ে শোনা যায়। এটি একটি শ্রুতিগ্রাহ্য (auditory) উপাদান। ধ্বনি ভাষার মৌখিক রূপের অংশ এবং এটি উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদাহরণ: ‘ক’ ধ্বনি বা ‘আ’ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শোনা যায়। ধ্বনির সংখ্যা ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।
বর্ণ:
বর্ণ হলো ধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্ন, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়। এটি একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) উপাদান। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ (যেমন: অ, আ, ই) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ (যেমন: ক, খ, গ) রয়েছে, যা ধ্বনিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করে।
উদাহরণ: যখন আমরা ‘ক’ উচ্চারণ করি, তখন তা ধ্বনি হিসেবে শোনা যায়, কিন্তু যখন লিখি ‘ক’, তখন তা বর্ণ হিসেবে দেখা যায়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ১৮. চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন-
ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঘ) সুকুমার সেন
সঠিক উত্তর: ঘ) সুকুমার সেন
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: ঘ) সুকুমার সেন।
ব্যাখ্যা:
চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, যা ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধ সহজিয়া পদাবলী। এই পদগুলো মূলত প্রাচীন বাংলা, মৈথিলি, ওড়িয়া, এবং অসমীয়ার মতো পূর্ব ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে রচিত। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় তিব্বতে, এবং এগুলো তিব্বতি ভাষায় অনুবাদিত বা টীকাকৃত আকারে পাওয়া যায়।
প্রেক্ষাপট:
• প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করছে যে চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো (২৩, ২৪, ২৫, এবং ৪৮ নং) তিব্বতি অনুবাদ থেকে প্রাচীন বাংলায় কে রূপান্তর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুসারে, এই কাজটি করেছেন সুকুমার সেন। তিনি আনুমানিকভাবে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেছেন।
• ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে ২৩ এর খণ্ডিত, ২৪, ২৫, এবং ৪৮ নং পদগুলো ছিল না।
• অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে,
মূল পুথির চারখানা পাতা লুপ্ত। এই চর্যাটির শেষ চার পঙ্ক্তি ও টীকা, ২৪ নং চর্যার সমস্ত অংশ ও টীকা এবং তার পরের অর্থাৎ ২৫ নং চর্যার মূল ও টীকার প্রথম অংশ বিনষ্ট। তবে এই চর্যাগুলির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সেই অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৪২ সালে। সেই অনুবাদ অবলম্বনে এই চর্যাগুলির মূল কী ছিল তা অনুমান করে একটি পাঠ-পরিকল্পনা দিয়েছেন ডক্টর হুকুমার সেন তাঁর ‘চর্যাীতি পদাবলী’ গ্রন্থের ৭৬ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠায়।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ভুল।
তিনি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীন বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর সাহিত্যিক ও ভাষাগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। তাঁর গবেষণা, বিশেষ করে The Origin and Development of the Bengali Language এবং চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এই কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য।
খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ভুল।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, কিন্তু তিনি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার বা রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিব্বতি অনুবাদ ১৯৫৬ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়।
গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র: ভুল।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) চর্যাপদ আবিষ্কারের (১৯০৭) অনেক আগে মারা যান। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করলেও চর্যাপদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।
ঘ) সুকুমার সেন: সঠিক।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে, সুকুমার সেন প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সংস্কৃত অনুবাদের ভিত্তিতে চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন এবং তা প্রকাশ করেন।
‘চর্যাপদ’ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
• বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।
• ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবার গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন।
• চর্যাপদের পদ সংখ্যা: চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫০টি। তবে সুকুমার সেন মনে করেন পদসংখ্যা ৫১টি।
• উদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা: চর্যাপদের সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া যায়।
• অনুদ্ধারকৃত/বিলুপ্ত পদের সংখ্যা: সাড়ে ৩টি। প্রাপ্ত সাড়ে ৪৬টি পদের মধ্যে ভুসুকুপা রচিত ২৩নং পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। পদটির ৬টি পদ পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি ৪টি পদ পাওয়া যায়নি।
• এছাড়াও চর্যাপদের ২৪নং (কাহ্নপা রচিত), ২৫নং (তন্ত্রীপা রচিত) এবং ৪৮নং (কুক্কুরীপা রচিত) পদগুলো পাওয়া যায়নি।
• চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র।
• ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি ভাষার অনুবাদ আবিষ্কার করেন।
• সংস্কৃত ভাষায় মুনিদত্ত চর্যাপদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি ১১নং পদের ব্যাখ্যা করেননি।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; চর্যাগীতি_পরিক্রমা- ড. নির্মল দাশ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন, Buddhist Mystic Songs- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১৯. ‘স্বাধীন’ শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) স্বীয়-এর অধীন খ) সত্ত্বার অধীন
গ) স্ব-এর অধীন ঘ) স্বত্তের-অধীন
সঠিক উত্তর: গ) স্ব-এর অধীন
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• সঠিক উত্তর – স্ব-এর অধীন। এটি একটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:
– পূর্বপদে যষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে।
যথা:
– চায়ের বাগান = চাবাগান,
– রাজার পুত্র = রাজপুত্র,
– খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।
– স্ব-এর অধীন = স্বাধীন।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- ৯ম ও ১০ম শ্রেণি (২০১৮ সংস্করণ) এবং বাংলা একাডেমি, অভিগম্য অভিধান।
প্রশ্ন ২০. ফররুখ আহমদের গ্রন্থ কোনটি?
ক) হরফের ছড়া খ) বর্ণশিক্ষা
গ) বর্ণপরিচয় ঘ) সহজ ছড়া
সঠিক উত্তর: ক) হরফের ছড়া
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো: ক) হরফের ছড়া।
‘হরফের ছড়া’ গ্রন্থ:
‘হরফের ছড়া’ ফররুখ আহমদের লেখা একটি বর্ণশিক্ষার বই, যা শিশুদের জন্য ছড়ার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।
অন্যদিকে,
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: তিনি ‘বর্ণপরিচয়’ নামে বিখ্যাত বর্ণশিক্ষার বই লিখেছেন। শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সহজ পাঠ’ নামে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।
‘বর্ণশিক্ষা’ বলতে কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।
ফররুখ আহমদ এর জীবিনী ও সাহিত্যকর্ম:
– ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
– ‘সাত সাগরের মাঝি’ ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
– ১৯৪৪ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ‘লাশ’ কবিতা লিখে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।
– ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত কাহিনী কাব্য ‘হাতেমতায়ী’ এর জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।
– ১৯৬৬ সালেই ‘পাখির বাসা’ শিশুতোষের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
– ‘মুহূর্তের কবিতা’ ফররুখ আহমদ রচিত একটি সনেট সংকলন।
তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থ:
– পাখির বাসা, হরফের ছড়া, নতুন লেখা, ছড়ার আসর, চিড়িয়াখানা, কিস্সা কাহিনী, মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড, ফুলের জলসা।
উৎস:
১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
২. বাংলাপিডিয়া।
৩. ‘হরফের ছড়া’ রচনা।
English Language and Literature
প্রশ্ন ২১. Pick the correctly spelt word:
ক) Conscintious খ) Consientious
গ) Concientious ঘ) Conscientious
সঠিক উত্তর: ঘ) Conscientious
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• The correctly spelt word: Conscientious.
• Conscientious (adjective):
– English Meaning: Meticulous, careful; Feeling a moral responsibility to do your work carefully and to be fair to others.
– Bangla Meaning: বিবেকবান; বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন।
• Example:
– A conscientious public servant.
– She has always been a very conscientious worker.Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ২২. They talked about going on a vacation’. Here ‘going’ is a/an-
ক) participle খ) infinitive
গ) verbal noun ঘ) gerund
সঠিক উত্তর: ঘ) gerund
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• They talked about going on a vacation.
– Here ‘going’ is a gerund.
– Here, “going” comes after the preposition “about”, so it must function as a noun.
– প্রদত্ত বাক্যে, going (verb+ing)- preposition “about” -এর object হিসেবে বসে noun -এর কাজ করেছে তাই এটি gerund.
– অর্থাৎ, ‘going’ এখানে যাওয়ার কাজ (an act or instance of going) বুঝাচ্ছে।
– এটি participle নয়, কারণ এই বাক্যে এটি কোনো noun/pronoun কে modify করেনি।
• Gerund:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
– সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
– Gerunds don’t describe action—they act as nouns.
• Functions of the Gerund:
1. As a subject of a verb: Rising early is a good habit.
2. As an object of a verb: I like reading poetry.
3. As an object of a preposition: I am tired of waiting.
4. As a complement of a verb: Seeing is believing.
5. As absolutely (part of a compound noun): This is my writing table.
অন্যদিকে,
• Present participle:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
– সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
– Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
– যেমন: Everything was in going order.
• Infinitive:
– Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
– যেমন: go, to go.
• Infinitive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
– To -যুক্ত infinitive এবং
– To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
– কোন বাক্যের Verb + ing – এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
– The + verb+ing + of = verbal noun.
– যেমন: The making of the plan is in hand.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.
প্রশ্ন ২৩. The novel ‘Wuthering Heights’ was penned by the author under the penname-
ক) Ellise Bellet খ) Ellis Belle
গ) Ellis Bell ঘ) Una Elis
সঠিক উত্তর: গ) Ellis Bell
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• The novel ‘Wuthering Heights’ was penned by the author under the pen name Ellis Bell.
• Wuthering Heights:
– Emily Bronte রচিত এই উপন্যাসটি ১৮৪৭ সালে Ellis Bell ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।
– ‘Heathcliff’ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন এতিম বালক।
– অন্যের আশ্রয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে আশ্রয়দাতার কন্যা Catherine Earnshaw -এর সাথে তার মনের মিলন ঘটে, দুইজন দুইজনকে ভালোবেসে ফেলে।
– কিন্তু Catherine প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অন্যত্র বিয়ে করলে Heathcliff নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
– যখন ফিরে আসে তখন সে অঢেল অর্থ বিত্তের মালিক।
– কাহিনীর এ পর্যায়ে তাকে তার মালিকের বাড়ি Wuthering Heights কিনে নেয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন প্রেমিকা Catherine -এর ননদের সাথে প্রেমের অভিনয় করে সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করতে দেখা যায়।
– পরবর্তীতে এই বিয়েটা ভেঙে যায় এবং এরপর Catherine মারা যায়। তার ভাই Hindley ও মারা যায়। কিন্তু তাদের সন্তানরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।
– Heathcliff -এর সন্তানও এদের সাথে যোগ দেয়। এভাবে কাহিনী এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের মাঝে এগিয়ে চলে।
– এটি ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ট্র্যাজেডি এবং Gothic Novel -এর একটি অন্যতম উদাহরণ।
• Main characters:
– Catherine Earnshaw,
– Cathy Linton,
– Edgar Linton,
– Heathcliff (The central character)
– Lockwood, etc.
• Emily Bronte (1818-1848):
– Emily Bronte ছিলেন একজন ইংরেজ লেখিকা ও কবি।
– তার পুরো নাম Emily Jane Bronte, তার ছদ্মনাম Ellis Bell.
– তিনি Charlotte Bronte -এর ছোট বোন।
– “Wuthering Heights” উপন্যাসকে ঘিরেই মূলত তার পরিচতি।
– মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই এই উপন্যাসিক মৃত্যু বরণ করেন।
• Notable Works:
– Poems by Currer, Ellis and Acton Bell,
– Wuthering Heights, etc.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ২৪. Which gender is the noun ‘neighbour’?
ক) Masculine খ) Feminine
গ) Neuter ঘ) Common
সঠিক উত্তর: ঘ) Common
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ‘Neighbour’ is a Common gender.
• Neighbour (noun, adjective, verb)
– English Meaning: one living or located near another.
– Bangla Meaning: প্রতিবেশী; প্রতিবাসী; পড়শি।- The noun “neighbour” refers to a person (male or female) who lives near or next to another.
• Common gender:
– A noun that denotes either a male or female is said to be of the common gender.- অর্থাৎ, Noun টি পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়কেই বুঝালে তা Common Gender হয়।
– যেমন: Infant (শিশু), Deer (হরিণ), student (ছাত্র/ছাত্রী), lawyer (উকিল), Neighbor (প্রতিবেশী), orphan (এতিম), parent (মা, বাবা), spouse (দম্পতি) etc.
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
প্রশ্ন ২৫. ‘Someone sneezed loudly at the back of the hall’.
In this sentence the verb ‘sneezed’ is-
ক) causative খ) intransitive
গ) transitive ঘ) factitive
সঠিক উত্তর: খ) intransitive
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ‘Someone sneezed loudly at the back of the hall’.
– In this sentence, the verb ‘sneezed’ is intransitive.
– “sneezed” এখানে Intransitive verb কারণ এটি কোনো Direct object গ্রহণ করেনি।
– Intransitive verb হলো এমন Verb যা কোন Direct object ছাড়াই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।
– The verb “sneezed” does not take a direct object – it expresses an action that does not pass over to an object.
– অর্থাৎ এটি কেবল subject -এর কাজ বোঝাচ্ছে, sneezed কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে (object) প্রভাবিত করছে না।
• Intransitive verb:
– An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object, or which expresses a state or being.
– অর্থাৎ, intransitive verb হলো subject নিজের দ্বারাই যে কাজ সম্পন্ন হয়, action (কাজ) সম্পন্ন হওয়ার জন্য object -এর দ্বারস্থ হতে হয় না।
– যে verb -এর কর্ম (direct object) নেই তাকে Intransitive verb বলে।
– এই verb কে ‘কি’ বা ‘কাকে’ দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না। Direct object থাকে না বলে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না।
– সাধারণত verb-এর পরে কোনো word না থাকলে অথবা verb-এর পরে adverb/preposition থাকলে সেটি Intransitive verb হবে।
• More Examples:
– The glass broke.
– We shall stop here a few days.
– The leaves fall in winter.
অন্যদিকে,
• Causative Verb:
– Subject যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় তখন এই অর্থে causative verb ব্যবহৃত হয়।
– Help, Get, Have, Let, Make ইত্যাদি বহুল প্রচলিত causative verb.
– Make, have, get প্রভৃতি যোগে অনেক verb- কে causative verb এ পরিণত করা যায়।
– যেমন: He always has me do his work. (সে সব সময় আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়।)
• Transitive verb:
– যে verb এর object আছে তাকে transitive verb বলে৷
– Transitive verbs এর সাধারণ Structure হচ্ছে: subject + verb + object.
– Object সর্বদাই Noun অথবা Pronoun হয়।
– তাই বাক্যে verb এর পরে Noun অথবা Pronoun থাকলে verb টি সাধারণত transitive verb হবে।
– আবার intransitive verb এর শেষে preposition + object যুক্ত করেও তাকে transitive verb এ পরিণত করা যায়।
– যেমন: He writes a letter. write হলো transitive verb, কারণ এর object হলো a letter.
• Factitive Verb:
– যে Verb এর Object বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে Factitive Verb বলে।
– Factitive Verb হলো এমন ক্রিয়া যা দুটি object নেয় – একটি direct object এবং একটি object complement।
– এই verb direct object কে object complement হিসেবে বর্ণিত অবস্থায় পরিণত করে বা নিয়োগ দেয়।
– কিছু factitive verbs হলো: Elect, Select, Make, Appoint, Call, Name, etc.
– যেমন: The manager appointed him secretary.
– উল্লিখিত বাক্যে secretary হচ্ছে Objective Complement Factitive Object.
– “The manager appointed him” দ্বারা বাক্য সম্পন্ন হচ্ছে না, তাই Objective Complement হিসেবে secretary বসানোর পর বাক্যটি সম্পন্ন হয়েছে।
– যেহেতু Object (him) বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়নি তাই এটি Factitive Verb.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.
প্রশ্ন ২৬. A person who leaves his/her own country to settle permanently in another is called a/an-
ক) immigrant খ) expatriate
গ) emigrant ঘ) migrant
সঠিক উত্তর: গ) emigrant
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• A person who leaves his/her own country to settle permanently in another is called an emigrant.
• Emigrant (Noun, Adjective)
– English Meaning: A person who leaves his/her own country to settle permanently in another country.
– Bangla Meaning: স্বদেশত্যাগী; বাস্তুত্যাগী বা দেশান্তরী (ব্যক্তি)।
অন্যদিকে,
• Immigrant (Noun):
– English Meaning: A person who comes to a country to take up permanent residence.
– Bangla Meaning: বহিরাগত; অভিবাসী; বসবাসের জন্য বিদেশে আগমনকারী।
• Expatriate (Noun, verb, adjective):
– English Meaning: A person who lives in a foreign country.
– Bangla Meaning: প্রবাসী ব্যক্তি।
• Migrant (Noun):
– English Meaning: A person who moves from one place to another, especially in order to find work or better living conditions; a bird or animal that migrates.
– Bangla Meaning: বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমনকারী (বিশেষত পাখি)।
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ২৭. Identify the word that can be used as both singular and plural:
ক) light খ) shot
গ) criterion ঘ) cannon
সঠিক উত্তর: ঘ) cannon
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• The correct answer is- ঘ) cannon.
• Cannon (Noun & Verb):
– English meaning: An old type of large, heavy gun, usually on wheels, that fires solid metal or stone balls.
– Bangla meaning: (collective; plural- এর স্থলে প্রায়ই ‘singular ব্যবহৃত হয়) (বিশেষত ধাতুর তৈরি নীরেট গোলানিক্ষেপক, প্রাচীন) কামান; আধুনিক সামরিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত গোলানিক্ষেপক ভারী, স্বয়ংক্রিয় কামান।
– Cannon -এর plural form হলো দুইটি- cannons or cannon.
– তবে সাধারণত plural হিসেবে cannon-ই ব্যবহার করা হয়।
– cannon (same form in military contexts).
অন্যদিকে,
• Light [uncountable noun] – আলোক; আলো → singular: light, plural: lights.
• Shot [countable noun] – গুলি; গুলিবর্ষণ; গুলির শব্দ → singular: shot, plural: shots.
– তবে ছোট সীসা বা ইস্পাতের গুলি, বিশেষ করে শটগানের জন্য চার্জ তৈরি করা অর্থে plural noun: shot ব্যবহৃত হয়।
– প্রচলিত plural form হলো- Shots.
– যেমন: Several shots were fired.
• Criterion (plural criteria বিচারের মাপকাঠি; মানদণ্ড) → singular: criterion, plural: criteria.
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ২৮. Identify the correct passive form, “People thought that the despot was corrupt”
ক) The despot had been thought to be corrupt.
খ) It was thought that the despot was corrupt.
গ) The despot was thought to be corrupt.
ঘ) The despot is thought to be corrupt.
সঠিক উত্তর: গ) The despot was thought to be corrupt.
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
– Active: People thought that the despot was corrupt.
– Passive: The despot was thought to be corrupt.
– এই ধরনের complex বাক্যে যেখানে that-clause আছে, সেখানে passive form তৈরির দুটি উপায় আছে:
– প্রথম উপায় (Impersonal passive) দ্বিতীয় অংশকে ‘It’ ধরে। যেমন:
– Active: People thought that the despot was corrupt.
– Passive: It was thought that the despot was corrupt.
– Subject হিসেবে People থাকলে Passive voice -এ সাধারণত তা লেখা হয় না।
– তবে, দ্বিতীয় অংশে transitive verb থাকলে দ্বিতীয় অংশেরও Passive করতে হয়।
– দ্বিতীয় উপায় (Personal passive):
– সাধারণত Acknowledge, assume, think, claim, believe, know, report, understand, ইত্যাদি verb যুক্ত Active voice এর Passive করার নিয়ম-
– Personal object টিকে subject ধরা হয়।
– Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে।
– মূল verb -এর past participle + to be + direct object + by + subject -এর objective form.
– যেমন:
– Active: People thought that the despot was corrupt.
– Passive: The despot was thought to be corrupt.
– তবে এই প্রশ্নে গ) অপশনটিই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে কারণ:
– Option গ) is more direct and commonly used when the focus is on the despot as the subject of the belief.
অন্যান্য অপশনগুলো বিশ্লেষণ:
ক) The despot had been thought to be corrupt.
– এটি ভুল কারণ, এখানে ভুল tense (had been = past perfect) ব্যবহার হয়েছে।
ঘ) The despot is thought to be corrupt.
– এটি ভুল কারণ, এখানে ভুল tense (is = present, কিন্তু মূল বাক্যে past tense) ব্যবহার হয়েছে।
প্রশ্ন ২৯. ‘After lunch we went for a leisurely stroll’. Here ‘leisurely’ is a /an-
ক) adverb খ) adjective
গ) noun ঘ) conjunction
সঠিক উত্তর: খ) adjective
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ‘After lunch we went for a leisurely stroll’.
– Here ‘leisurely’ is an adjective.
– The word “leisurely” describes the noun “stroll” — it tells what kind of stroll it was.
– When a word modifies a noun, it functions as an adjective.
– অর্থাৎ, ‘leisurely’ শব্দটি noun ‘stroll’ এর আগে বসে এটিকে বর্ণনা করছে।• Leisurely (adjective)
– English Meaning: acting or done at leisure; unhurried or relaxed.
– Bangla Meaning: ব্যস্ততাহীন।
• Leisurely (adverb)
– English Meaning: without haste: deliberately.
– Bangla Meaning: মন্থরগতিতে; ধীরে ধীরে; ব্যস্ততাহীনভাবে।
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ৩০. The play “Englishmen for My Money” was written by-
ক) Christopher Marlowe খ) Thomas Kyd
গ) William Haughton ঘ) Ben Jonson
সঠিক উত্তর: গ) William Haughton
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• The play “Englishmen for My Money” was written by William Haughton.
• Englishmen For My Money: Or A Woman Will Have Her Will:
– Englishmen for My Money, or A Woman Will Have Her Will হলো এলিজাবেথীয় যুগের একটি কমেডি নাটক, যা ১৫৯৮ সালে William Haughton রচনা করেছিলেন।
– Scholars and critics often cite it as the first city comedy.
– এই নাটকটি একটি dramatic subgenre সূচনা করেছিল, যা পরবর্তীতে Thomas Dekker, Thomas Middleton, Ben Jonson, এবং অন্যান্যরা পরবর্তী বছর ও দশকে আরও প্রসারিত ও উন্নত করেছিলেন।
• Summary:
– গল্পটি আবর্তিত হয় এক ধনী বিধবা মিসেস ফ্লাওয়ারডেলকে নিয়ে, যাকে তিনজন পুরুষ – স্যার লিওনেল ফ্রিভিল, স্যার থমাস লং এবং মাস্টার গ্যালিয়ার্ড – এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রতিটি পুরুষ তার স্নেহ ও ভাগ্য জয়ের চেষ্টা করে, কিন্তু মিসেস ফ্লাওয়ারডেল তার নিজের পথ নির্ধারণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সে এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয় যে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। নাটকটি সেই সময়ের সামাজিক রীতিনীতি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতার উপর একটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিনোদনমূলক দৃষ্টিপাত। হটনের লেখনী ধারালো ও হাস্যরসাত্মক, এবং চরিত্রগুলি সুসংহত ও স্মরণীয়।
• William Haughton (1575-1605):
– William Haughton ছিলেন এলিজাবেথীয় যুগের একজন ইংরেজ নাট্যকার।
– তিনি ১৫৯৭ থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এবং প্রখ্যাত Admiral’s Men (a theatrical company) নাট্যকোম্পানির জন্য নাটক লিখতেন।
– He collaborated in many plays with Henry Chettle, Thomas Dekker, John Day and Richard Hathway.
– তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক হলো “Englishmen For My Money”, এই নাটকটিকেই ইংরেজি ভাষার প্রথম প্রহসন-ভিত্তিক শহুরে কমেডি (City Comedy) হিসেবে ধরা হয়।
• Notable works:
– Englishmen For My Money,
– The Devil and His Dame,
– The English Moor, etc.
Source:
1. Britannica.
2. Goodreads.com
প্রশ্ন ৩১. “… I cannot but conclude the Bulk of your Natives, to be the most pernicious race of little odious vermin that Nature ever suffered to crawl upon the surface of the Earth”. the statement occurs in
ক) Robinson Crusoe খ) A Doll’s House
গ) Vanity Fair ঘ) Gulliver’s Travels
সঠিক উত্তর: ঘ) Gulliver’s Travels
Live MCQ Analytics™: Right: 18%; Wrong: 4%; Unanswered: 76%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
“… I cannot but conclude the Bulk of your Natives, to be the most pernicious race of little odious vermin that Nature ever suffered to crawl upon the surface of the Earth”. – এই উক্তিটি এসেছে Jonathan Swift-এর বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক রচনা Gulliver’s Travels থেকে।
• Gulliver’s Travels:
– Jonathan Swift রচিত একটি novel, তিনি Augustan age এর একজন Author, তাই এটি Augustan age এর রচনা।
– এটি 18th century এর একটি famous satire.
– এটি ৪ খন্ডের একটি রম্য রচনা।
– এর full title হচ্ছে – Travels into Several Remote Places in the World.
– এই novel টি ১৭২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
• Lemuel Gulliver সমুদ্র ভ্রমণে বের হয় এবং পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ভেঙ্গে যায়।
– Gulliver প্রানে বেঁচে যায় কিন্তু এক অদ্ভুত দেশে নিজেকে আবিষ্কার করে যেখানে সবার উচ্চতা ৬ ইঞ্চির নিচে।
– তার বিশাল দেহ নিয়ে লিলিপুটদের নানা উপকারে আসে, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য Blefuscu এর সাথে চলমান যুদ্ধেও লড়াই করে।
– এভাবে সে লিলিপুটদের রাজ্যে একপ্রকার হিরোতে পরিণত হয়।
– যদিও এক পর্যায়ে Gulliver তাদের রোষের শিকার হয় এবং তার শাস্তি হয় তার চোখ তুলে ফেলা হবে।
– পরিশেষে Gulliver শাস্তি এড়াতে সমর্থ হয় এবং বেঁচে ফিরে আসে।
• Jonathan Swift:
– তিনি একজন Anglo-Irish author এবং clergyman ছিলেন।
– তিনি Augustan age এর একজন Author.
– Jonathon Swift, an Anglo-Irish author, who was the foremost prose satirist in the English language.
– অর্থাৎ, ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যঙ্গরচয়িতা বা satirist হলেন Jonathan Swift.
– তার রচিত বিখ্যাত satire হলো ‘Gulliver’s Travels’.
– তাঁর ছদ্মনাম Isaac Bickerstaff.
• Famous works:
– Gulliver’s Travels,
– A Tale of a Tub,
– A Modest Proposal,
– The Battle of Books.
Other options,
ক) Robinson Crusoe
লেখক: Daniel Defoe.
খ) A Doll’s House
লেখক: Henrik Ibsen.
গ) Vanity Fair
লেখক: William Makepeace Thackeray.
Source: Britannica & Live MCQ lecture.
প্রশ্ন ৩২. ‘We know that the earth is a planet‘. The underlined part is a/an-
ক) noun clause খ) adverbial clause
গ) adjective clause ঘ) principal clause.
সঠিক উত্তর: ক) noun clause
Live MCQ Analytics™: Right: 71%; Wrong: 10%; Unanswered: 18%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
We know that the earth is a planet. The underlined part is a/an – Noun clause.
– এখানে “that the earth is a planet” অংশটি ‘know’ verb -এর object হিসেবে কাজ করছে।• Noun clause:
– যে সব subordinate- clause noun এর কাজ করে থাকে অর্থাৎ, subject, object, compliment, বা case in apposition- এর কাজ করে থাকে তাদেরকে বলে noun clause.
– Noun clauses are used when a single word isn’t enough.
• একটি বাক্যের যেসব স্থানে Noun clause বসতে পারে –
1. Verb এর subject হিসেবে।
Example: That he has much money is known to all.
2. Verb এর object হিসেবে।
Example: I know that he has done it.
3. Verb এর complement হিসেবে।
Example: This is what I said.
4. Preposition এর object হিসেবে;
Example: I cannot understand the meaning of what he said.
5. Noun/ pronoun – এর apposition হিসেবে।
Example: The fact that he is a thief is clear to all.
Source:
– A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain.
– Advanced Learner’s Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.
প্রশ্ন ৩৩. Select the sentence in which ‘better’ is an adverb.
ক) We’re helping for better weather tomorrow.
খ) Sound travels better in water than in air.
গ) It’s hard to decide which one is better.
ঘ) He joined the gym to better his health.
সঠিক উত্তর: খ) Sound travels better in water than in air.
Live MCQ Analytics™: Right: 50%; Wrong: 20%; Unanswered: 28%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো খ) Sound travels better in water than in air.
– এই বাক্যে ‘better’ শব্দটি ‘travels’ verb কে বর্ণনা করছে।
– এটি বলছে শব্দ কীভাবে ভ্রমণ করে।
– অর্থাৎ, “শব্দ পানিতে বেশি ভালোভাবে ভ্রমণ করে”।
– যেহেতু এটি verb কে modify করছে, তাই এটি adverb.
Better: [adverb]
English meaning: in a more excellent or pleasant way; to a higher or greater degree.
Bangla meaning: কোনো কাজ বা পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো বা বেশি আনন্দদায়কভাবে ঘটেছে।
Example:
– She sings much better than I do.
– Sound travels better in water than in air.
Other options,
ক) We’re hoping for better weather tomorrow.
– ‘better’ এখানে adjective.
– এটি noun ‘weather’ কে বর্ণনা করছে।
গ) It’s hard to decide which one is better.
– এখানে better হচ্ছে adjective।
– এখানে “better” শব্দটি “which one” কে বর্ণনা করছে।
– এটি verb ‘is’ এর পরে complement হিসেবে এসেছে।
ঘ) He joined the gym to better his health.
– এখানে better হলো verb, অর্থাৎ “উন্নত করা”।
Source:
– Oxford Dictionary.
প্রশ্ন ৩৪. Fill in the blanks with appropriate words. ‘Selina knocked it _______ the park with her performance in culinary art.
ক) outside খ) out of
গ) inside ঘ) off
সঠিক উত্তর: খ) out of
Live MCQ Analytics™: Right: 27%; Wrong: 26%; Unanswered: 46%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর হলো খ) out of.
Complete sentence: Selina knocked it out of the park with her performance in culinary art.
Bangla: সেলিনা রান্নার শিল্পে তার পারফরম্যান্স দিয়ে অসাধারণ সফলতা পেয়েছে/দুর্দান্ত করেছে।
knock sb/sth out of the park: [idiom]
English meaning: to do something much better than someone else, or to be much better than someone or something else/ to do something extremely well.
Bangla meaning: কারো চেয়ে অনেক ভালো কিছু করা, বা কারো/কিছুর চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করা/ কোনো কাজ চরমভাবে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা।
Example:
– Hotel Ferrero knocks everyone out of the park with their breakfast.
– The BBC is hitting them all out of the park at the moment, in children’s drama at least.
– I feel like I can write anything for this actor, and she’ll knock it out of the park.
– If I don’t hit this out of the park, I’m finished.
সঠিক idiom টি হলো – knock out of the park তাই উল্লিখিত অন্য অপশন গুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
Source:
– Cambridge Dictionary.
প্রশ্ন ৩৫. The idiom ‘icing on the cake’ means –
ক) a slice of the cake
খ) an attractive but unnecessary addition
গ) an attractive service
ঘ) an attractive and essential enhancement
সঠিক উত্তর: খ) an attractive but unnecessary addition
Live MCQ Analytics™: Right: 48%; Wrong: 11%; Unanswered: 39%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর – খ) an attractive but unnecessary addition.
• The icing on the cake: [idiom]
English meaning: If you describe something as the icing on the cake, you mean that it makes a good thing even better, but it is not essential.
Bangla meaning: এর মানে হলো এটি ইতিমধ্যেই ভালো কিছুকে আরও ভালো করে তোলে, কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়।
Example:
– I was just content to see my daughter in such a stable relationship, but a grandchild, that really was the icing on the cake.
– I love my job, and getting public recognition is merely the icing on the cake.
– The third goal was the icing on the cake.
Other options,
ক) a slice of the cake:
→ কেকের একটি টুকরো।
খ) an attractive but unnecessary addition:
→ আকর্ষণীয় কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সংযোজন।
গ) an attractive service:
→ আকর্ষণীয় সেবা।
ঘ) an attractive and essential enhancement:
→ আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন।
অপশন গুলোর অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায়, সঠিক উত্তর – খ) an attractive but unnecessary addition.
Source:
– Cambridge Dictionary.
– Collins Dictionary.
প্রশ্ন ৩৬. Choose the synonym for ‘fright’:
ক) placidity খ) composure
গ) apprehension ঘ) equanimity
সঠিক উত্তর: গ) apprehension
Live MCQ Analytics™: Right: 15%; Wrong: 11%; Unanswered: 73%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: গ) apprehension.
• Fright: [noun]
English meaning: the feeling of fear, especially if felt suddenly, or an experience of fear that happens suddenly.
Bangla meaning: আকস্মিক প্রচণ্ড ভীতি; আতঙ্ক; ত্রাস; সন্ত্রাস; শঙ্কা।
Other options,
ক) Placidity: [noun]
English meaning: the fact of being calm and peaceful, with very little movement.
Bangla meaning: শান্ততা; প্রসন্নতা।
খ) Composure: [noun]
English meaning: the state of being calm and in control of your feelings or behaviour.
Bangla meaning: শান্তি; স্থৈর্য; আত্মসংবরণ।
গ) Apprehension: [noun]
English meaning:
– worry about the future, or a fear that something unpleasant is going to happen.
– an act of catching and arresting someone who has not obeyed the law.
– the act of understanding something, or the way that something is understood.
Bangla meaning:
– [Countable noun, Uncountable noun] আশঙ্কা; ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠার অনুভূতি: filled with apprehension; an apprehension of failure.
– [Uncountable noun] (আইন সম্বন্ধীয়) গ্রেফতার: the apprehension of a thief.
– [Uncountable noun] উপলব্ধি; চেতনা; বোধ: apprehension of truth.
ঘ) Equanimity: [noun]
English meaning: a calm mental state, especially after a shock or disappointment or in a difficult situation
Bangla meaning: মনমেজাজের প্রশান্তি।
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, Fright এর synonym হলো – Apprehension.
Source:
– Cambridge Dictionary.
– Accessible Dictionary.
– Oxford Dictionary.
প্রশ্ন ৩৭. “Rubiyat of Khayyam” is attributed to
ক) Edward FitzGerald খ) Scott Fitzgerald
গ) Thomas Fitzgerald ঘ) William Fitzgerald
সঠিক উত্তর: ক) Edward FitzGerald
Live MCQ Analytics™: Right: 38%; Wrong: 13%; Unanswered: 47%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সাহিত্য কর্মটির সঠিক নাম – The Rubaiyat of Omar Khayyam.
• The Rubaiyat of Omar Khayyam:
– এটি রচনা করেন সাহিত্যিক Edward Fitzgerald.
– যুগ শ্রেষ্ঠ জ্যেতির্বিজ্ঞানী ওমার খৈয়ামের রচনা থেকে অনুপ্রাণিত।
– এটি মূলত: অনুবাদ নয় বরং মূল গ্রন্থকে সামনে রেখে মৌলিক রচনা।
– এটি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি Classic হিসেবে বিবেচিত।
– It is one of the most frequently quoted lyric poems, and many of its phrases are passed into common currency.
– প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।
– ইংরেজি সংস্করণে এই নামের সাথে যুক্ত হয়- “the Astronomer-Poet of Persia” বাক্যটি।
• Edward Fitzgerald:
– Edward Fitzgerald belongs to the Victorian Period.
– He was born on March 31, 1809, in England.
– FitzGerald was educated at Trinity College, Cambridge, where he formed a lifelong friendship with William Makepeace Thackeray.
• Notable Work:
– The Rubaiyat of Omar Khayyam.
Source: Live MCQ English Essence and Britannica.
প্রশ্ন ৩৮. ‘We work every day except Friday’. In this sentence ‘except’ is a/an
ক) adjective
খ) noun
গ) preposition
ঘ) pronoun
সঠিক উত্তর: গ) preposition
Live MCQ Analytics™: Right: 70%; Wrong: 9%; Unanswered: 19%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
We work every day except Friday. In this sentence, ‘except’ is a/an – Preposition.
– এখানে except শব্দটি বোঝাচ্ছে “Friday-এর বাইরে” বা “Friday ছাড়া”।
– অর্থাৎ এটি Friday-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যা হলো preposition-এর কাজ।
– এটি দেখাচ্ছে যে শুক্রবার ছাড়া বাকি সব দিন কাজ হয়।
• Except: [preposition]
English meaning: used before you mention the only thing or person about which a statement is not true.
Bangla meaning: ব্যতীত; ছাড়া।
Example:
– We work every day except Sunday.
– They all came except Matt.
– I had nothing on except for my socks.
Source:
– Oxford Dictionary.
– Accessible Dictionary.
প্রশ্ন ৩৯. Who wrote “A Vindication of the Rights of Women”?
ক) Claire Clairmont
খ) Marry Wollstonecraft
গ) Mary Wollstonecraft Godwin
ঘ) Mary Shelley
সঠিক উত্তর: গ) Mary Wollstonecraft Godwin
Live MCQ Analytics™: Right: 4%; Wrong: 10%; Unanswered: 84%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
A Vindication of the Rights of Woman:
– এটি রচনা করেন British writer Mary Wollstonecraft Godwin.
– এটি ১৭৯২ সালে প্রকাশিত একটি প্রসিদ্ধ নারীবিদ্বেষ-বিরোধী প্রবন্ধ, যা ব্রিটিশ লেখক এবং নারী অধিকার কর্মী Mary Wollstonecraft লিখেছেন।
– এই রচনায় নারীদের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ এবং বিবাহে ক্ষমতায়ন (empowerment) নিশ্চিত করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।
Mary Wollstonecraft/ Mary Wollstonecraft Godwin:
– জন্ম ২৭ এপ্রিল, ১৭৫৯, লন্ডন, ইংল্যান্ড — মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭, লন্ডন।
– তিনি ছিলেন একজন ইংরেজি লেখিকা এবং নারীদের শিক্ষাগত ও সামাজিক সমতার প্রবল সমর্থক। তিনি তার বিশ্বাসসমূহ “A Vindication of the Rights of Woman” (১৭৯২) গ্রন্থে উপস্থাপন করেন, যা নারীবাদ (ফেমিনিজম)-এর একটি ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত।
Notable works:
– A Vindication of the Rights of Woman,
– Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark,
– Maria; or, The Wrongs of Woman.
Other option,
খ) Marry Wollstonecraft: Marry ভুল বানান, সঠিক বানান হলো – Mary Wollstonecraft.
উল্লেখ্য –
• Mary Wollstonecraft:
– Married name: Mary Wollstonecraft Godwin is actually her full married name, but she is generally known as Mary Wollstonecraft.
– Spouse name: William Godwin.
– Daughter: Mary Wollstonecraft Shelley.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৪০. Which sentence is correct?
ক) The picture was hanged on the wall.
খ) The picture was hung on the wall.
গ) The picture was hunged on the wall.
ঘ) The picture had hanged on the wall.
সঠিক উত্তর: খ) The picture was hung on the wall.
Live MCQ Analytics™: Right: 45%; Wrong: 30%; Unanswered: 23%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: খ) The picture was hung on the wall.
“Hang” verb এর past tense ও past participle আলাদা ব্যবহারে বিভক্ত।
• Hang(verb) ঝোলা; ঝুলে থাকা; ঝুলানো; ঝুলিয়ে রাখা।
– এই অর্থে এর past tense, past participle form হবে Hung.
– hang something from the ceiling; a picture hanging on the wall; windows hung with curtains.
• Hang (verb) ফাঁসি দেওয়া; ফাঁসি হওয়া; ফাঁসি নেওয়া
– এই অর্থে এর past tense, past participle form hanged হবে।
– He was hanged for murder, খুনের দায়ে ফাঁসি হয়েছে;
– He hanged himself, ফাঁস নিয়ে মরেছে।
অর্থাৎ, যখন কোনো ছবি বা বস্তু দেওয়ালে ঝুলানো হয়, তখন past tense ও past participle হলো hung.
– যখন কারো ফাঁসিতে ঝুলানো হয়, তখন past tense ও past participle হলো hanged.
• যেহেতু এখানে ছবি দেয়ালে ঝুলানো হয়েছে, তাই সঠিক ব্যবহার হবে: was hung.
Other options,
ক) The picture was hanged on the wall.
– Hanged ব্যবহার হয় ফাঁসিতে ঝুলানো এর জন্য, যেমন Execution-এর ক্ষেত্রে।
– এখানে ছবির প্রসঙ্গ, তাই ভুল।
খ) The picture was hunged on the wall.
– এখানে, Hunged হলো ভুল বানান; English-এ hung হলো সঠিক past participle.
ঘ) The picture had hanged on the wall.
– hanged ফাঁসির জন্য ব্যবহৃত হয়।
– এছাড়া, past perfect tense “had hanged” এখানে প্রয়োজন নেই, কারণ সাধারণ description দেওয়া হচ্ছে।
Source:
– Accessible Dictionary.
বাংলাদেশ বিষয়াবলি
প্রশ্ন ৪১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভুমিকা পালন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘তমুদ্দুন মজলিস’। তমুদ্দুন মজলিস-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন?
ক) রসায়ন খ) পদার্থ বিজ্ঞান
গ) অর্থনীতি ঘ) ইসলামী শিক্ষা
সঠিক উত্তর: খ) পদার্থ বিজ্ঞান
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ ‘তমদ্দুন মজলিস’-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
♦ তমদ্দুন মজলিশ:
→ তমদ্দুন মজলিশ ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।
→ তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শাশ্রয়ী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
→ ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
→ মদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক এ.এস.এম নূরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, হাসান ইকবাল
→ অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তমদ্দুন মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হন।
→ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বস্তুত তমদ্দুন মজলিশই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
→ এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।
→ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে তমদ্দুন মজলিশের প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম ছিল ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’।
→ তমদ্দুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
→ ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন।
→ পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়।
→ এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৪২. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি?
ক) ২৬ মার্চ খ) ২১ ফেব্রুয়ারী
গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ৫ আগস্ট
সঠিক উত্তর: ক) ২৬ মার্চ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস।
♦ স্বাধীনতা দিবস:
→ ১৯৮০ সালের ৩ অক্টোবর ২৬ শে মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
→ ১৯৮১ সাল থেকে ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
→ ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সেজন্যে একে স্বাধীনতা দিবস বলা হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
→ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস।
→ ৫ আগস্ট ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’।
♦ বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস:
→ ০২ মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস।
→ ০১ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস।
→ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস।
→ ১৬ জুলাই ‘জুলাই শহীদ দিবস’।
তথ্যসূত্র – জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৪৩. নিম্নোক্ত কোন ভারতীয় রাজ্যের বাংলাদেশের সাথে কোন ভূমি সীমানা নাই?
ক) নাগাল্যান্ড খ) মিজোরাম
গ) মেঘালয় ঘ) আসাম
সঠিক উত্তর: ক) নাগাল্যান্ড
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোন ভূমি সীমানা নেই।
♦ বাংলাদেশের সীমান্ত:
→ বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। যথা:
• ভারত ও
• মিয়ানমার।
→ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা: ৩২টি।
→ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা: ৩০টি।
→ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা: ৩টি।
→ বাংলাদেশ-ভারত ও মায়ানমার এই তিনটি দেশের যৌথ সীমান্ত রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলার।
♦ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত:
→ ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪১৪২ কিলোমিটার।
→ এটি পৃথিবীর ৫ম দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমারেখা।
→ বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সীমান্ত আছে।
→ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্যসমূহ: আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ।
তথ্যসূত্র – জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ওয়ার্ল্ড এটলাস ও Statistica.com
প্রশ্ন ৪৪. আয়নাঘর কী?
ক) স্বচ্ছ কামরা খ) পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজ
গ) গোপন কারাগার ঘ) একটি হলিউড মুভি
সঠিক উত্তর: গ) গোপন কারাগার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ আয়নাঘর দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার অধীনে পরিচালিত ‘গোপন কারাগার’।
♦ আয়নাঘর:
→ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাউন্টার-টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিটিআইবি) দ্বারা পরিচালিত একটি গোপন আটক কেন্দ্রের নাম আয়নাঘর।
→ আয়নাঘর দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার অধীনে পরিচালিত হয়।
→ এটি রাজনৈতিক বিরোধীদের, সরকার-সমালোচকদের, সন্দেহভাজন ‘চরমপন্থী’ বা ‘সন্ত্রাসী’দের গুম করে আটক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
→ মূলত সরকার-বিরোধী চক্রান্তে সন্দেহভাজনদের আটক রাখা হত এখানে।
→ শুধু তৎকালীন সরকারের সমালোচকেরা নন, ‘চরমপন্থী’ বা ‘সন্ত্রাসবাদী’ হিসাবে চিহ্নিত করেও বহু মানুষকে ‘আয়নাঘর’ বা সেই জাতীয় গোপন বন্দিশালাগুলিতে আটক করা হয়েছিল।
♦ আয়নাঘরের অবস্থান:
→ আয়নাঘরের অবস্থান ঢাকা সেনানিবাস এলাকায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে, যেখানে প্রাচীর-আবৃত অন্ধকার কক্ষসমূহ ছিল।
→ এতে কমপক্ষে ১৬টি কক্ষ রয়েছে, প্রতিটিতে ৩০ জন করে বন্দি রাখার সক্ষমতা রয়েছে।
♦ উল্লেখ্য:
→ ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিদেশি গণমাধ্যমকর্মী ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে বহুল আলোচিত ‘আয়নাঘর’ পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
→ রাজধানীর আগারগাঁও, কচুক্ষেত ও উত্তরা এলাকায় তিনটি স্পট পরিদর্শন করেন তিনি।
তথ্যসূত্র – পত্রিকার রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৪৫. বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নিম্নের কোন অধিকারটি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক) বাক-স্বাধীনতার অধিকার খ) শিক্ষার অধিকার
গ) সভা সমাবেশের অধিকার ঘ) ধর্মচর্চার অধিকার
সঠিক উত্তর: খ) শিক্ষার অধিকার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।
♦ বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়:
→ বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মৌলিক অধিকার।
→ বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বাক-স্বাধীনতার অধিকার, সভা সমাবেশের অধিকার ও ধর্মচর্চার অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
♦ তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সমূহ:
→ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার।
♦ বাংলাদেশ সংবিধানের ১১টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ:
• প্রথম অধ্যায় – প্রজাতন্ত্র।
• দ্বিতীয় অধ্যায় – রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।
• তৃতীয় অধ্যায় – মৌলিক অধিকার।
• চতুর্থ অধ্যায় – নির্বাহী বিভাগ।
• পঞ্চম অধ্যায় – আইনসভা।
• ষষ্ঠ অধ্যায় – বিচার বিভাগ।
• সপ্তম অধ্যায় – নির্বাচন।
• অষ্টম অধ্যায় – মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
• নবম অধ্যায় – বাংলাদেশের কর্মবিভাগ।
• দশম অধ্যায় – সংবিধানের সংশোধন।
• একাদশ অধ্যায় – বিবিধ।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের সংবিধান।
প্রশ্ন ৪৬. ‘কম-দামে কেনা বেশী দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা’-বইটির লেখক কে?
ক) আবুল কালাম শামসূদ্দীন খ) আবুল মনসুর আহমদ
গ) শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঘ) এস ওয়াজেদ আলী
সঠিক উত্তর: খ) আবুল মনসুর আহমদ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা:
→ ‘বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা’ গ্রন্থের লেখক আবুল মনসুর আহমেদ।
→ ‘বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা’ গ্রন্থে যে ৪২টি নিবন্ধ রয়েছে।
→ সেগুলির মধ্যে প্রথম ৩৯টি ১৯৭২ ও ৭৩ সালে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক ‘ইত্তেফাক’-এ প্রকাশিত হয়েছে।
→ এই গ্রন্থে প্রকাশিত ৪২-টি নিবন্ধ পাচ মিশালা হহলেও প্রত্যেকাঢর মূল বক্তব্য অভিন্ন।
→ প্রবন্ধগুলোতে নানান দিকে উদ্ভুত জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরই পথ-নির্দেশনা লেখক তার লেখাগুলো দিয়েছেন।
→ অনেক বিষয়ে তিনি লেখা ও আলোচনা শুরু করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সবার উপর।♦ আবুল মনসুর আহমেদ:
→ তিনি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
→ আবুল মনসুর আহমদ একজন সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক।
→ তিনি খিলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।
♦ ব্যঙ্গরচনা:
→ আয়না,
→ ফুড কনফারেন্স,
→ গালিভারের সফরনামা
♦ স্মৃতিকথা:
→ আত্মকথা (১৯৭৮, আত্মজীবনী),
→ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,
→ শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু।
♦ তাঁর রচিত উপন্যাস:
→ সত্যমিথ্যা,
→ জীবন ক্ষুধা,
→ আবে-হায়াৎ
তথ্যসূত্র – বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৪৭. ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেনদরবার করার ক্ষেত্রে কোন নেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
ক) হাকিম আজমল খান
খ) শেরে বাংলা এ, কে. ফজলুল হক
গ) স্যার সলিমুল্লাহ
ঘ) স্যার আব্দুর রহিম
সঠিক উত্তর: গ) স্যার সলিমুল্লাহ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেনদরবার করার ক্ষেত্রে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকার রমনা এলাকায় নিজ জমি দান করেন।
→ বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকায় ‘সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন’ এবং ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির’ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
→ নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন।
→ ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করেন।
→ ৩১ জানুয়ারি নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে একটি মানপত্র প্রদান করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
→ ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এক ইশতেহারে ভারত সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ ঘোষণা করা হয়।
– ১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান হয়ে আসছে।
তথ্যসূত্র – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা জেলা ওয়েবসাইট এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৪৮. সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম কী?
ক) Parliament খ) National Parliament
গ) Legislature ঘ) The House of the Nation
সঠিক উত্তর: ঘ) The House of the Nation
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম ‘The House of the Nation’.
→ সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইনসভার উল্লেখ রয়েছে।
→ সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।
♦ জাতীয় সংসদ:
→ জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।
→ দেশের সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এ সংসদের ওপর ন্যস্ত।
→ প্রতি নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।
→ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে (২০১১) মহিলা আসন সংখ্যা ৫০ করা হয়।
→ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি।
→ জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।
→ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহবান করা হয়।
→ জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য কোরাম থাকতে হয়।
→ অধিবেশনে কোরামের জন্য ন্যূনতম ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।
→ সংবিধান অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ চলবে অর্থাৎ ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কোরাম হবে।
→ ৬০ জনের কম সদস্য উপস্থিত থাকলে স্পিকার সংসদের অধিবেশন স্থগিত রাখেন।
তথ্যসূত্র – বাংলাপিডিয়া ও বাংলাদেশের সংবিধান।
প্রশ্ন ৪৯. জিএসপি (GSP) এর পূর্ণ রূপ কী?
ক) Generalized System of Preference
খ) Global System of Positioning
গ) Global Strategic Partnership
ঘ) Government Support Program
সঠিক উত্তর: ক) Generalized System of Preference
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ জিএসপি (GSP) এর পূর্ণরূপ ‘Generalized System of Preferences’.
♦ GSP:
→ Generalized System of Preferences (GSP) হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া এক ধরণের শুল্কমুক্ত বা শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা।
→ GSP হচ্ছে পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার।
→ ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রথম GSP সুবিধা চালু করে।
→ নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম জিএসপি সুবিধা দেয় ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬ সালে।
→ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারায় ২৭ জুন, ২০১৩ সালে।
→ যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা পাবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত।
তথ্যসূত্র – ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েবসাইট, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইট, পত্রিকা রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৫০. চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব কি?
ক) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ
খ) সংসদের আসন বৃদ্ধি
গ) সংরক্ষিত নারী আসন বাতিল
ঘ) পি আর (PR) চালু করা
সঠিক উত্তর: ক) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ।
♦ সংস্কার প্রস্তাব:
→ এই সংস্কারে বর্তমান এককক্ষ সংসদের পরিবর্তে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) গঠিত হবে।
→ যাতে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও সুষ্ঠু, জনকেন্দ্রিক এবং চেক-অ্যান্ড-ব্যালেন্স সহ নিশ্চিত হয়।
→ নিম্নকক্ষে ৪০০ সদস্য (৩০০ সরাসরি নির্বাচিত + ১০০ নারী সংরক্ষিত সরাসরি নির্বাচিত) এবং উচ্চকক্ষে ১০৫ সদস্য (১০০ সমানুপাতিক + ৫ রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন, ৩০% নারী সংরক্ষিত) থাকবে।
♦ উল্লেখ্য:
→ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনার লক্ষ্যে প্রস্তাব তৈরির জন্য ২০২৪ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে সরকার।
→ সেগুলো হলো সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কমিশন।
→ সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
→ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই কমিশনের সভাপতি।
তথ্যসূত্র – পত্রিকার রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৫১. বাংলাদেশের ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স অনুযায়ী সর্ব প্রথম কে অবস্থান করেন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) প্রধান উপদেষ্টা ঘ) প্রধান বিচারপতি
সঠিক উত্তর: খ) রাষ্ট্রপতি
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স অনুযায়ী:
রাষ্ট্রপতি (President of the Republic) এর অবস্থান সর্ব প্রথম।
উল্লেখ্য,
২. প্রধানমন্ত্রী
৩. সংসদের স্পিকার
৪. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগণ।
৫. কেবিনেট মন্ত্রিগণ; কেবিনেটের প্রধান হুইপ; সংসদের ডেপুটি স্পিকার; সংসদে বিরোধী দলের নেতা
৬. কেবল পদমর্যাদা অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সমমানের পদে থাকা ব্যক্তিরা।
৭. বিশেষ দূত ও কমনওয়েলথ দেশের হাইকমিশনারগণ, যারা বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত।
৮. প্রধান নির্বাচন কমিশনার; পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান; সংসদে বিরোধী দলের ডেপুটি নেতা;সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ(আপিল বিভাগ); রাষ্ট্রের রাজ্য মন্ত্রীগণ; হুইপ।
এছাড়াও,
ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে মোট ২৫টি পদক্রম রয়েছে।
উৎস: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৫২. পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
ক) বিচারপতি সাত্তার খ) বিচারপতি সায়েম
গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঘ) বিচারপতি হামদুর রহমান
সঠিক উত্তর: ক) বিচারপতি সাত্তার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার।
১৯৭০ এর নির্বাচন:
– ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
– অবশ্য ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দুর্গত ও উপকূলীয় এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৭ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।
– নির্বাচনে মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
– ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট বরাদ্দ ছিল ১৬৯টি আসন।
– জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭টি সংরক্ষিত আসন সহ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে।
– প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০০টি সাধারণ আসন ও ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট ৩১০টি আসন বরাদ্দ ছিল।
– প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি সাধারন আসন ও ১০টি সংরক্ষিত আসন সহ মোট ২৯৮টি আসন লাভ করে।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, মোজাম্মেল হক ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৫৩. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক চা বাগান রয়েছে কোন জেলায়?
ক) সিলেট খ) চট্টগ্রাম
গ) মৌলভীবাজার ঘ) পঞ্চগড়
সঠিক উত্তর: গ) মৌলভীবাজার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• চা-বাগান:
– চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধকৃত দেশে মোট চা-বাগানের সংখ্যা – ১৭০ টি।
– মৌলভীবাজার জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ৯০ টি।
– হবিগঞ্জ জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ২৫ টি।
– সিলেট জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ১৯ টি।
– চট্টগ্রাম জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ২২ টি।
– রাঙ্গামাটি জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ২ টি।
– পঞ্চগড় জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ১১ টি।
– ঠাকুরগাওঁ জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা – ১ টি।
– খাগড়াছড়ি জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা -১ টি
উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৫৪. চীন, ভারত ও বাংলাদেশের প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী, চীন বা তিব্বতে কী নামে পরিচিত?
ক) ইয়াংসি খ) লিজিয়াং
গ) হয়াইলি ঘ) ইয়ারলাং সাংপো
সঠিক উত্তর: ঘ) ইয়ারলাং সাংপো
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ইয়ারলাং সাংপো” (Yarlung Tsangpo):
– ব্রহ্মপুত্র নদী এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী এবং এটি তিনটি দেশের মধ্যে প্রবাহিত: চীন, ভারত, এবং বাংলাদেশ।
– ব্রহ্মপুত্র নদী চীনের তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং সেখানে এ নদীকে “ইয়ারলাং সাংপো” (Yarlung Tsangpo) নামে ডাকা হয়।
– পরে এটি ভারতে প্রবেশ করে “সিয়াং” নামে পরিচিত হয় এবং বাংলাদেশে এসে “ব্রহ্মপুত্র” নামে প্রবাহিত হয়।
উল্লেখ্য,
– সম্প্রতি, চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতের ভূখণ্ডে ইয়ারলাং সাংপো” (Yarlung Tsangpo) নদীতে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে। – এমন একটি প্রকল্প যা ভারতের ও বাংলাদেশের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
উৎস: ব্রিটানিকা ও বিবিসি নিউজ।
প্রশ্ন ৫৫. বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের শহীদ আবু সাঈদ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ) রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়
গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
সঠিক উত্তর: ঘ) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• শহীদ আবু সাঈদ:
– রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা বাবনপুর গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেন এর ঘরে জন্ম নেয় আবু সাঈদ।
– আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।
– তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন।
– ২০২৪ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে ১৬ জুলাই দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্ক মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন আবু সাঈদ।
– ১৬ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়কে পুলিশ আবু সাঈদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে।
– আবু সাঈদ এক হাতে লাঠি নিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দেন।
– কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লুটিয়ে পড়েন।
উৎস: প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার।
প্রশ্ন ৫৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?
ক) তথ্য মন্ত্রণালয়
খ) প্রেস কাউন্সিল
গ) বিটিআরসি
ঘ) বাংলাদেশ টেলিভিশন
সঠিক উত্তর: খ) প্রেস কাউন্সিল
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
⇒ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রেস কাউন্সিল।
♦ প্রেস কাউন্সিল:
→ প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মানোন্নয়ন ও মান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়।
→ প্রেস কাউন্সিল একটি আধা-বিচারিক সংস্থা।
→ প্রেস কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাদের মান উন্নত ও বজায় রাখা।
♦ প্রেস কাউন্সিলের কার্যাবলী:
• সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করা।
• উচ্চ পেশাগত মান অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।
• সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের দ্বারা জনসাধারণের উচ্চমানের রুচি বজায় রাখা এবং নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
• সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব বৃদ্ধি করা।
• জনস্বার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সরবরাহ ও প্রচারে বাধা সৃষ্টিকারী যেকোনো উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
• সাংবাদিকতা পেশায় ব্যক্তিদের জন্য সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা।
তথ্যসূত্র –
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ওয়েবসাইট।
Media Landscapes
প্রশ্ন ৫৭. Demographic Dividend বলতে কী বুঝায়?
ক) শিশু মৃত্যুহার হ্রাস
খ) জন্মহার শূনের কোটায় আনা
গ) জনসংখ্যার অধিকাংশ বেকার
ঘ) কর্মক্ষম বয়স গোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি
সঠিক উত্তর: ঘ) কর্মক্ষম বয়স গোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড:
– যখন একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার পরিমাণ দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক হয় তখন তাকে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
– জনসংখ্যার এরূপ অবস্থায় নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (১৫ বছরের কম ও ৬৪) সংখ্যা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অপেক্ষা কম হয়।
– বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ অবস্থা অতিবাহিত করছে।
– বিবিএসের জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২–এর সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৯১১ জন।
– তার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা হলো ১১ কোটি ৭ লাখ প্রায়, যা মোট জনসংখ্যার ৬৫.২৩ শতাংশ।
– জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তথ্যানুসারে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ভোগ করবে।
– জনসংখ্যার এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হলে একটি দেশ দ্রুত উন্নয়ন সাধন করতে পারে।
উৎস: বিবিএস ও জাতিসংঘ ওয়েসাইট এবং প্রথম আলো।
প্রশ্ন ৫৮. ভাষা-পরিবার অনুযায়ী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত কোন পরিবার ভুক্ত?
ক) ইন্দো-আর্য খ) দ্রাবিড়
গ) অস্ট্রিক-অস্ট্রো এসিয়াটিক (মুন্ডা) ঘ) তিব্বত-বর্মী
সঠিক উত্তর: গ) অস্ট্রিক-অস্ট্রো এসিয়াটিক (মুন্ডা)
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
সাঁওতাল:
– সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী।
– তাদের বাসস্থান মূলত রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়।
– প্রধান নিবাস রাঢ়বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর; পরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাঁওতাল পরগনায়।
– সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর।
– সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদি বাসিন্দা, এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষিসংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।
সাঁওতালরা খুবই উৎসবপ্রিয় জাতি। বাঙালিদের মতো এদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রায় প্রতিমাসে বা ঋতুতে রয়েছে পরব বা উৎসব যা নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
নববর্ষের মাস ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত হয় স্যালসেই উৎসব,
– চৈত্রে বোঙ্গাবোঙ্গি,
– বৈশাখে হোম,
– আশ্বিনে দিবি,
– পৌষ শেষে সোহরাই উৎসব পালিত হয়।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৫৯. লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল হওয়ায় পূর্বে কোন্ ভূমিকায় ছিলেন?
ক) ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী
খ) ফ্রান্সে নিযুক্ত ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত
গ) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান
ঘ) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
সঠিক উত্তর: গ) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
• লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের গভর্নর-জেনারেল হওয়ার আগে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
• চার্লস কর্নওয়ালিস:
সেভেন ইয়ার্স ওয়ার (১৭৫৬–৬৩)-এর একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন কর্নওয়ালিস।
এই যুদ্ধে (১৭৬২ সালে) তিনি তার পিতার আর্ল উপাধি ও অন্যান্য পদবি উত্তরাধিকার সূত্রে পান।
তিনি যদিও উত্তর আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করেছিলেন, তবুও তিনি আমেরিকান বিপ্লব দমন করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।
– ১৭৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনের দেশপ্রেমিক বাহিনীকে নিউ জার্সি থেকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু ১৭৭৭ সালের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন আবার রাজ্যের একটি অংশ পুনর্দখল করেন।
– ১৭৮০ সালের জুন মাসে দক্ষিণাঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নওয়ালিস জেনারেল হোরেশিও গেটসের বিরুদ্ধে সাউথ ক্যারোলিনার ক্যামডেনে (১৬ আগস্ট, ১৭৮০) এক বড় জয় লাভ করেন।
– পূর্ব নর্থ ক্যারোলিনা হয়ে ভার্জিনিয়ায় অগ্রসর হয়ে তিনি জোয়ারভাটার বন্দর নগর ইয়র্কটাউনে তার ঘাঁটি স্থাপন করেন।
– সেখানে তিনি আমেরিকান ও ফরাসি স্থলবাহিনীর (ওয়াশিংটন ও কমতে দ্য রোশামবো এর নেতৃত্বে) এবং ফরাসি নৌবাহিনীর (কমতে দ্য গ্রাস এর নেতৃত্বে) দ্বারা অবরুদ্ধ হন।
– অবশেষে তিনি এক দীর্ঘ অবরোধের পর তার বিশাল সেনাবাহিনীসহ আত্মসমর্পণ করেন।
– যদিও ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণের ঘটনাটি যুদ্ধকে উপনিবেশবাসীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত করে দেয়, তবুও কর্নওয়ালিস নিজ দেশে উচ্চ মর্যাদা বজায় রাখেন।
– ১৭৮৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন।
উৎস: ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ৬০. আশিস নন্দী, শশী থারুর প্রমুখ লেখকের মতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা কোন সংঘটনটি?
ক) মুসলিম লীগ খ) সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
গ) আর.এস.এস. ঘ) জমিয়তে-ই-হিন্দ
সঠিক উত্তর: ক) মুসলিম লীগ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব:
→ দ্বি-জাতি তত্ত্ব হলো একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার মতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবনাচার ও ভিন্ন ঐতিহ্যের কারণে একই জাতি নয়; তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। তাই তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা আবশ্যক।
দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আশিস নন্দী, শশী থারু প্রমুখ :
– আশিস নন্দী, শশী থারুর প্রমুখ লেখকের মতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা মুসলিম লীগ।
– তারা আরও মনে করেন যে পাকিস্তান চাওয়া মুসলিম লীগের দাবি ছিল, কংগ্রেসের নয়।
– মূলত তাদের মতে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর জিন্নাহর দ্বিজাতি ত্বত্তের ১৬ বছর পূর্বে দ্বিজাতি ত্বত্ত প্রদান করেছিলনে।
– এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি।
– প্রসঙ্গত, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে বলেছে যে, “নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (CAB) প্রয়োজন হয়েছিল কারণ কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করেছিল।”
– এর উত্তরে শশী থারুর প্রশ্ন করছেন, “অমিত শাহ কি ইতিহাস জানেন না? জিন্নাহ, দুই-জাতির তত্ত্ব, মুসলিম লীগের পাকিস্তান রেজোলিউশন এসব কি তিনি জানেন না? বাস্তবে পাকিস্তান চাওয়া মুসলিম লীগের দাবি ছিল, কংগ্রেসের নয়।”♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও সৈয়দ আহমদ খান এর ভূমিকা:
→ সৈয়দ সায়্যদ আহমদ খান মীরাটে ১৬ মার্চ ১৮৮৮ সালের এক বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলিমকে আলাদা করে ‘two nations’ উল্লেখ করেন; এই মীরাট-বক্তৃতাই আধুনিক ‘দ্বি-জাতি’ ধারণার সবচেয়ে প্রাথমিক স্পষ্ট রূপগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।
→ মীরাটে দেওয়া বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ খান স্পষ্টভাবে বলেন: ‘হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায়, যাদের ধর্ম, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা ভিন্ন। একটি যৌথ রাষ্ট্রে তাদের একসঙ্গে শাসন করা কঠিন হবে।’
→ মীরাট বক্তব্যে সৈয়দ সরাসরি আলাদা রাষ্ট্র দাবি করেননি; তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতা-অসাম্য তুলে ধরেছিলেন।
→ তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আলাদা।
→ এই বক্তৃতা এবং তাঁর অন্যান্য লেখনীতে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর এই ধারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।• জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব:
– জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি জনগোষ্ঠীকে তখনই জাতি বলা যায়, যার ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মনন, কৃষ্টি, ধর্ম এমনকি অর্থনীতি একটি একক সত্তায় পরিণতি লাভ করে।
– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দুটি পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটিই মূলত জিন্নাহর ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’।
– ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ্ তাঁর ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ ঘোষণা করেন।
– পরবর্তী বছর লাহোরে মুসলিম লীগের ঘোষণায় এরই প্রতিধ্বনি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।
– ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্।
– এ অধিবেশনেই বাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
– এতে বলা হয় যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি একটি নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আল্লামা ইকবাল এর ভূমিকা:
→ ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল এলাহাবাদে All India Muslim Legue-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন।
→ এই ভাষণে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে একত্র করে স্বশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।
→ তাঁর কবিতা ও রচনা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয় জাগ্রত করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
→ ইতিহাসবিদদের মতে, স্যার সাইয়্যদের বপন করা বীজকে ইকবাল দার্শনিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেন, যা পরবর্তীতে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ নেয়।উৎস:
i) Shashitharoor Website। [Link]
ii)The Demonic and the Seductive in Religious Nationalism: Vinayak Damodar Savarkar and the Rites of Exorcism in Secularizing South Asia by Ashis Nandy। [Link]
iii) ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iv) বাংলাপিডিয়া, ব্রিটানিকা ও কয়েকটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।
v) Dwan ওয়েবসাইট।
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
প্রশ্ন ৬১. নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সামরিক জোট কত সালে সাক্ষরিত হয়?
ক) ১৯৩৯ খ) ১৯৪৩
গ) ১৯৪৯ ঘ) ১৯৬০
সঠিক উত্তর: গ) ১৯৪৯
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সামরিক জোট ১৯৪৯ সালে সাক্ষরিত হয়।
NATO:
– NATO-এর পূর্ণরূপ:North Atlantic Treaty Organisation অথবা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট।
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে NATO গঠিত হয়।
– ন্যাটো মূলত সামরিক সহযোগিতার জোট।
– প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।
– প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ১২টি।
– বর্তমান সদস্য: ৩২টি।
– সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
– বর্তমান মহাসচিব: মার্ক রুট্টে।
– মুসলিম দেশ: আলবেনিয়া ও তুরস্ক।
⇒ ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে এক চুক্তির মাধ্যমে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল।
– এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের হাত থেকে পশ্চিম বার্লিন এবং ইউরোপের নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করা।
– ন্যাটো একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি, যে চুক্তির আওতায় জোটভুক্ত দেশগুলো পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
– এর প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র তাদের সামরিক বাহিনীকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখতে বদ্ধপরিকর।
– এছাড়াও, ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিটি ১৪টি ধারার।
উৎস: NATO ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৬২. বাংলাদেশ-ICCPR এর স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ICCPR এর পূর্ণরূপ কী?
ক) International Conference on Civil and Political Rights
খ) International Conference of Civil and Political Rights
গ) International Covenant on Civil and Political Rights
ঘ) International Covenant of Civil and Political Rights
সঠিক উত্তর: গ) International Covenant on Civil and Political Rights
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ বাংলাদেশ-ICCPR এর স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ICCPR এর পূর্ণরূপ International Covenant on Civil and Political Rights.
ICCPR:
– ICCPR-এর পূর্ণরূপ: International Covenant on Civil and Political Rights.
⇒ এটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি।
– গৃহীত হয়: ১৯৬৬ সালে।
– কার্যকর হয়: ২৩ মার্চ, ১৯৭৬ সালে।
– আন্তর্জাতিক এই চুক্তি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
– বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি পেশার এবং প্রতিটি মানুষ যেন সমান অধিকার পায় সেই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে দুইটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
– এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যেমন-জীবনের অধিকার, বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচারের অধিকার সুরক্ষা করা।
– এতে মোট ৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
– এই চুক্তি বাস্তবায়ন তদারকি করে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি (UN Human Rights Committee)।
উল্লেখ্য,
– বাংলাদেশ এটি ২০০০ সালে অনুমোদন করে।
উৎস: UN ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৬৩. গ্রিনল্যান্ড নিচের কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত?
ক) সুইডেন খ) ডেনমার্ক
গ) নরওয়ে ঘ) ফিনল্যান্ড
সঠিক উত্তর: খ) ডেনমার্ক
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত।
গ্রিনল্যান্ড:
– গ্রিনল্যান্ড বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ।
– এটি ডেনমার্কের একটি স্বশাসিত অঞ্চল।
– গ্রিনল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অংশ।
– এর অবস্থান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত।
– এর অবস্থান কানাডা এবং আইসল্যান্ডের মাঝে অবস্থিত।
– আয়তনে মূল ডেনমার্কের চেয়ে গ্রীনল্যান্ড প্রায় ৫০ গুন বড়।
– রাজধানী: নুউক।
– গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা এস্কিমো হিসেবে পরিচিত।
উল্লেখ্য,
– গ্রিনল্যান্ড ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ ছিল। ১৯৭৯ সালে গণভোটের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল, তবে দ্বীপটির পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি এখনও ডেনমার্কই দেখভাল করে।
– এ দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে তেল ও গ্যাস। আরও আছে পৃথিবীর বিরল কিছু ধাতু, যেগুলোর বৈদ্যুতিক গাড়ি ও বায়ুকলের পাশাপাশি সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে উচ্চ চাহিদা রয়েছে।
উৎস: i) Britannica.
ii) BBC.
প্রশ্ন ৬৪. বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন; ‘বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারনা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়” এই ঐতিহাসিকের নাম কি?
ক) এন্থনি মাসকারেনহাস খ) লরেঞ্চ জিরিং
গ) লরেঞ্চ লিফশূলজ্ ঘ) হেনরি কিসিঞ্জার
সঠিক উত্তর: খ) লরেঞ্চ জিরিং
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন; ‘বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারনা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়” এই ঐতিহাসিকের নাম লরেঞ্চ জিরিং।
অধ্যাপক লরেঞ্চ জিরিং:
– ‘বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারণা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়’- লরেঞ্চ জিরিং (Lawrence Ziring) কর্তৃক প্রদত্ত।
– তিনি তাঁর গ্রন্থ ‘বাংলাদেশ: মুজিব থেকে এরশাদ: একটি বিশ্লেষনধর্মী ইতিহাস’-এই গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণ করেছেন।
– যেখানে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেছেন।
– এই গ্রন্থে জিরিং উল্লেখ করেছেন যে, স্বাধীনতার প্রথম বিশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যারা জনগণের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বা ধারণার ভিত্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
– মূলত এটি একটি নিরপেক্ষ ইতিহাসের বই। ১৯৪০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বাঙালি রাজনৈতিক নেতা, তাঁদের শাসনকাল, তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা/অস্থিরতা সহ বিভিন্ন বিষয় নিরপেক্ষভাবে উঠে এসেছে।
⇒ এছাড়াও, তিনি “মুজিব, এরশাদ ও হাসিনা: রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ইতিহাস” নামক একটি বইয়ের লেখক।
Link: core.ac.uk page: 124.
উৎস: বাংলাদেশ: মুজিব থেকে এরশাদ: একটি বিশ্লেষনধর্মী ইতিহাস।
প্রশ্ন ৬৫. বিশ্বের প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কোনটি?
ক) UNOSOM খ) UNMOGIP
গ) UNTSO ঘ) UNEF
সঠিক উত্তর: গ) UNTSO
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ বিশ্বের প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization).
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন:
– জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (United Nations Peacekeeping Mission) একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যা সংঘাতপ্রবণ দেশগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।
– এই মিশনের প্রধান লক্ষ্য হলো সংঘর্ষমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, মানবাধিকার রক্ষা করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনায় সহায়তা করা।
– বর্তমানে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে জাতিসংঘের ১১টি শান্তিরক্ষা মিশন চলমান রয়েছে।
– এগুলো হলো: MINURSO (পশ্চিম সাহারা), MINUSCA (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র), MONUSCO (গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র), UNDOF (গোলান হাইটস), UNFICYP (সাইপ্রাস), UNIFIL (লেবানন), UNISFA (আবিয়েই), UNMIK (কসোভো), UNMISS (দক্ষিণ সুদান), UNMOGIP (ভারত ও পাকিস্তান), UNTSO (মধ্যপ্রাচ্য)।
⇒ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মূল উদ্দেশ্য:
– সংঘাতের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সশস্ত্র বিরোধী পক্ষদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করা।
– যুদ্ধ বা সংঘাতের কারণে বিপর্যস্ত জনগণের জন্য মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া।
– রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ মিশন আঞ্চলিক সরকারের সহায়তায় কাজ করে থাকে।
– যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনা, যেমন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি।
উল্লেখ্য,
– ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয়।
– ১৯৪৮ সালে সংঘটিত ১ম আরব-ইসরাইল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন অনুষ্ঠিত হয়।
– এই মিশনের নাম ছিল “United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)”।
– এটি ছিল জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা।
এছাড়াও,
– জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৮ সালে।
উৎস: United Nations Peacekeeping ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৬৬. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়?
ক) প্যারিস চুক্তি খ) ভারসাই চুক্তি
গ) জেনেভা চুক্তি ঘ) রোম চুক্তি
সঠিক উত্তর: খ) ভারসাই চুক্তি
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি:
– বিধ্বংসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
– স্থান: ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদের হল অফ মিররসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
– পক্ষসমূহ: মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান) এবং জার্মানি।
– প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ওপর যে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছিল, তা মূলত স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles)-এর মাধ্যমে হয়েছিল। এই চুক্তিটি জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে এবং মিত্র দেশগুলোর ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।
– ফলাফল: যুদ্ধের কারণে মিত্র দেশগুলোর যে ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্য জার্মানিকে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
• প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:
– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (World War I) ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ।
– যুদ্ধটি মূলত ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘটিত হলেও এর প্রভাব ছিল পৃথিবীজুড়ে।
⇒ যুদ্ধের পটভূমি:
– যুদ্ধ শুরু হয়: ২৮ জুলাই, ১৯১৪ সালে।
– শেষ হয়: ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ সালে।
– যুদ্ধের ফলাফল: মিত্র শক্তির বিজয়।
– অক্ষশক্তি: জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়া।
– মিত্রশক্তি: সার্বিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশ।
উৎস: i) History.com
ii) Britannica.
প্রশ্ন ৬৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন?
ক) হাঁরি এস. ট্রুম্যান খ) ফ্রাঙ্কলিন ডি, বুজভেল্ট
গ) রিচার্ড নিক্সন ঘ) জর্জ ডারিও বুশ
সঠিক উত্তর: ক) হাঁরি এস. ট্রুম্যান
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি এস. ট্রুম্যান জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন।
হ্যারি এস. ট্রুম্যান:
– হ্যারি এস. ট্রুম্যান (Harry S. Truman) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম রাষ্ট্রপতি।
– তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
– তিনি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি থেকে রাষ্ট্রপতিত্বে উন্নীত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে শীতল যুদ্ধের উত্থান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নেতৃত্ব দেন।
– হ্যারি এস. ট্রুম্যান জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন।
উল্লেখ্য,- পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই প্রকল্পের নাম ছিল ‘ম্যানহাটান প্রজেক্ট’। পারমাণবিক বোমার জনক রবার্ট ওপেনহেইমার ছিলেন ম্যানহাটান প্রজেক্টের প্রধান।
– জাপানের দুটি শহরে এই বোমা ফেলার পর বিপুল প্রাণহানি আর ধ্বংসলীলা ঘটেছিল।
– ৩৩তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান এই পারমাণবিক বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেন।⇒ লিটলবয় ও ফ্যাটম্যান:
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় শেষের পথে, তখন আগস্টের জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র।
– বিশ্বে প্রথম কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র। মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ।
– জাপানের হিরোশিমা শহরে ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে বোমা বর্ষণ করে। নিক্ষিপ্ত বোমাটির নাম ছিলো লিটলবয়।
– ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে। নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির নাম ছিলো ফ্যাটম্যান।
উৎস: History.com
প্রশ্ন ৬৮. ODS (Ozone Depleting Substances) এর ব্যবহার কমানোর জন্য কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক) কিয়োটো প্রটোকল খ) মন্ট্রিল প্রটোকল
গ) প্যারিস চুক্তি ঘ) রামসার কনভেনশন
সঠিক উত্তর: খ) মন্ট্রিল প্রটোকল
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ ODS (Ozone Depleting Substances) এর ব্যবহার কমানোর জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।
⇒ ODS (Ozone Depleting Substances) হলো এমন পদার্থ যা সাধারণত রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং অ্যারোসলের মতো পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
মন্ট্রিল প্রটোকল:
– Montreal Protocol-এর পূর্ণরূপ: The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
– মন্ট্রিল প্রোটোকল হল ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থ (ODS) ব্যবহার এবং উৎপাদন বন্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।
– মন্ট্রিল প্রোটকলের মূখ্য আলোচ্য বিষয়: ওজোন স্তরের সুরক্ষা।
⇒ চুক্তি গৃহীত হয়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সালে।
– কার্যকর হয়: ১ জানুয়ারী, ১৯৮৯ সালে।
– চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান: মন্ট্রিল, কানাডা।
– চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ: ২০০টি।
– চুক্তি অনুমোদনকারী দেশ: ১৯৮টি।
উল্লেখ্য,
– ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি), হ্যালন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফর্ম, মিথাইল ব্রোমাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোব্রোমোফ্লোরোকার্বন ইত্যাদি গ্যাসের প্রভাবে দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে এই ওজোন স্তর। যার ফলে তৈরি হচ্ছে ওজোন হোল বা গর্ত। প্রায় সকল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) ই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ও এর বিকল্পসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এ গ্যাসগুলো সাধারণতঃ রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমে, এ্যাজমা চিকিৎসায় উৎপাদিত ইনহেলারে, ফ্যান, প্লাস্টিক ফোম তৈরি ও মাইক্রোইলেকট্রিক সার্কিট পরিস্কার করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য ওজোনস্তর রক্ষায় কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ওজোনস্তরের ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
– ধরিত্রীকে রক্ষার লক্ষ্যে ওজোনস্তর রক্ষায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে ‘ভিয়েনা কনভেনশন’ গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে “মন্ট্রিল প্রটোকল” নামে এক যুগান্তকারী চুক্তি গৃহীত হয়।
উৎস: i) UNEP ওয়েবসাইট।
ii) Ozone Secretariat।
ii) তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)।
প্রশ্ন ৬৯. আফিম যুদ্ধ কোন দুইটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়?
ক) চীন ও আফগানিস্তান খ) চীন ও ইংল্যান্ড
গ) চীন ও রাশিয়া ঘ) ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান
সঠিক উত্তর: খ) চীন ও ইংল্যান্ড
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ আফিম যুদ্ধ চীন ও ইংল্যান্ড- এই দুইটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।
আফিম যুদ্ধ:
– আফিমের চোরাচালানকে কেন্দ্র করে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাই আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত।
– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উনিশ শতকের গোড়া থেকে চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ে ঘাটতি মেটাতে বঙ্গদেশ থেকে চীনে আফিম রপ্তানি শুরু করে।
– চীনা শাসকরা ১৮৩৯ সালে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
– কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবৈধ উপায়ে এ ব্যবসা অব্যাহত রাখে।
– কোম্পানির অবৈধ আফিম ব্যবসার কারণে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।
– ১ম যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয় এবং চীন ১৮৪২ সালে নানকিং চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
• নানকিং চুক্তি:
– প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনের শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের সাথে একটি অপমানজনক ‘অসম চুক্তি’ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
– এই চুক্তির নাম নানকিং চুক্তি।
– চিনা কমিশনার চিইং (Chiying) এবং নব নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি পট্টিনগার (Sir Henry Pottinger) -এর উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
– চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: ২৯ আগস্ট, ১৮৪২ সালে
– এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশদের হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল।
– এছাড়া চীন কর্তৃক ব্রিটেনকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য হয়।
– পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালে চীন সরকার ৯৯ বছরের জন্যে হংকংকে ব্রিটেনের নিকট লিজ দেয় এবং ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই লিজের মেয়াদ শেষে ব্রিটেন পুনরায় চীনের নিকট হংকং কে হস্তান্তর করে।
উৎস: Britannica.
প্রশ্ন ৭০. কেপ ভারদ (Cape Verde) দ্বীপ রাষ্ট্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক) গালফ অফ গিনি খ) ফ্রেঞ্ছ পলিনেশিয়া
গ) দক্ষিন আফ্রিকা ঘ) পশ্চিম আফ্রিকা
সঠিক উত্তর: ঘ) পশ্চিম আফ্রিকা
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ কেপ ভারদ (Cape Verde) দ্বীপ রাষ্ট্রটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত।
কেপ ভার্দে (Cape Verde):
– কেপ ভার্দে রাষ্ট্রটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত।
– এটি আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ।
– রাজধানী: প্রাইয়া (Praia)।
– সরকারি ভাষা: পর্তুগিজ।
– মুদ্রা: কেপ ভার্দীয় এসকুডো (সিভিই)।
– ধর্ম: খ্রিস্টধর্ম (প্রধানত রোমান ক্যাথলিক); এছাড়াও ইসলাম।
– এর রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি এবং এর সরকারপ্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।
উল্লেখ্য,
– কেপ ভার্দে পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
উৎস: Britannica.
প্রশ্ন ৭১. নিম্নোক্ত কোন দেশ বা অঞ্চল জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয়?
ক) তিমুর লিস্টি খ) দক্ষিন সুদান
গ) ওয়েস্টার্ন সাহারা ঘ) সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক
সঠিক উত্তর: গ) ওয়েস্টার্ন সাহারা
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ ওয়েস্টার্ন সাহারা জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয়। তিমুর লিস্টি, দক্ষিন সুদান ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক জাতিসংঘের সদস্য দেশ।
ওয়েস্টার্ন সাহারা (পশ্চিম সাহারা):
– পশ্চিম সাহারা বা ওয়েস্টার্ন সাহারা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন জনবহুল অঞ্চল যার বেশিরভাগই মরুভূমি।
– বৃহত্তম শহর: লায়াউন।
– ওয়েস্টার্ন সাহারা একটি বিতর্কিত অঞ্চল।
– এটি পূর্বে স্পেনের উপনিবেশ (Spanish Sahara) ছিল। ১৯৭৫ সালে তা স্বাধীন হয়। কিন্তু মরক্কো ওই এলাকার অনেকটাই দখল করে নেয়। তখন থেকে পশ্চিম সাহারার স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছে মরক্কোর।
– দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে সংঘর্ষ চলছে। পশ্চিম সাহারার স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের নাম পোলিসারিও ফ্রন্ট। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত লাগাতার যুদ্ধ চলার পর মরক্কো এবং পোলিসারিও-র মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সই হয়। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে পোলিসারিও নতুন করে লড়াই শুরু করেছে।
– ওয়েস্টার্ন সাহারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র নয়। জাতিসংঘ এই অঞ্চলকে “Non-self-governing territory” হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।অন্যদিকে,- তিমুর-লিস্টি (পূর্ব তিমুর) ২০০২ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
– দক্ষিণ সুদান ২০১১ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
– সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ১৯৬০ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
⇒ জাতিসংঘ:
– বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা হলো জাতিসংঘ (United Nations Organization).
– এটি জাতিপুঞ্জের (League of Nations) উত্তরসূরী।
– জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়: ২৬ জুন, ১৯৪৫।
– জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়: ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
– স্বাক্ষরের স্থান: যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো।
– প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ৫১টি।
– বর্তমান সদস্য: ১৯৩টি।
– সর্বশেষ সদস্য: দক্ষিণ সুদান।
– বর্তমান মহাসচিব: আন্তোনিও গুতেরেস।
– সদর দপ্তর: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
– দাপ্তরিক ভাষা ৬টি: ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ এবং আরবি।
– কার্যকরী দাপ্তরিক ভাষা ২টি: ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট।
ii) Britannica.
প্রশ্ন ৭২. নিম্নোক্ত কোন দেশটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য নয়?
ক) বুলগেরিয়া খ) হাঙ্গেরি
গ) পোল্যান্ড ঘ) সুইজারল্যান্ড
সঠিক উত্তর: ঘ) সুইজারল্যান্ড
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য নয়। অন্যদিকে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union):
– বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
– প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
– সদরদপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
– প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ: ৬টি।
– ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ: ২৭টি।
⇒ ইইউ দেশগুলো হলো: অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া , স্লোভেনিয়া, স্পেন এবং সুইডেন।
উল্লেখ্য,
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে।
• ১৮ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে প্যারিসে একচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ (ECSE- European Coal and Steel Community) গঠিত হয়।
• ২৫ মার্চ, ১৯৫৭ সালে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস্, ইতালি ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানী এ ৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ‘রোম চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়।
– এ চুক্তি অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে European Economic Community (EEC) এবং Euratom প্রতিষ্ঠিত হয়।
• পরবর্তীতে EEC একটি একক ইউরোপিয় অর্থনীতি গঠন করার প্রয়াস চালায়।
– ১৯৬৫ সালে সম্পাদিত ‘ব্রাসেলস চুক্তি’ সংগঠনটিকে European Community (EC) রূপান্তরিত করে।
• ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত ‘ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি’র ভিত্তিতে EC রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন European Union (EU) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
এছাড়াও,
– শেনজেনভুক্ত দেশ: ২৯টি।
– ইউরো মুদ্রা ব্যবহারকারী দেশ: ২০টি।
উৎস: EU ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৭৩. নিম্নোক্ত কোন দেশটি ‘Five Eyes’ ভুক্ত নয়?
ক) অস্ট্রেলিয়া খ) ফ্রান্স
গ) নিউজিল্যান্ড ঘ) কানাডা
সঠিক উত্তর: খ) ফ্রান্স
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ ‘Five Eyes’ গোয়েন্দা জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশ নয় ফ্রান্স। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা Five Eyes-এর সদস্য।
Five Eyes:
– Five Eyes ইন্টেলিজেন্স অ্যালায়েন্স, যা FVEY নামেও পরিচিত।
– ‘এটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের একটি গোয়েন্দা জোট।
– জোটটি UKUSA চুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
– তারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে কাজ করে।
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তারা তাদের দেশকে নিরাপদ রাখতে একে অপরকে সাহায্য করছে।
– সন্ত্রাসবাদ, সাইবার হুমকি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য তারা শেয়ার করে।
⇒ UKUSA চুক্তি:
– ১৯৪৩ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য একটি সমবায় গোয়েন্দা চুক্তি গঠন করে যা BRUSA চুক্তি নামে পরিচিত।
– এই গোপন চুক্তিটি পরবর্তীতে UKUSA চুক্তি হিসাবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
– এই চুক্তিটি ফাইভ আই দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের ভিত্তি স্থাপন করে।
উৎস: Five Eyes ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৭৪. “কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারন”-অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কোন গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন?
ক) Development as Freedom
খ) Women and Human Development
গ) Development through Disposition
ঘ) Development, Environment and Power
সঠিক উত্তর: ক) Development as Freedom
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ “কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারন”- অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ‘Development as Freedom’ গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন।
অমর্ত্য সেন:
– অমর্ত্য সেন একজন ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক।
– ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।
– দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান অমর্ত্য সেন।
⇒ ১৯৫১ সালে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং তারপর অর্থনীতি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। এছাড়াও তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
– তিনি ইকোনমিস্ট ফর পিস অ্যান্ড সিকিউরিটির একজন ট্রাষ্টি।
– তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষাবিদ যিনি একটি অক্সব্রিজ কলেজের প্রধান হন। এছাড়াও তিনি প্রস্তাবিত নালন্দা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবেও কাজ করেছেন।
– ২০০৬ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে অনূর্ধ্ব ষাট বছর বয়সী ভারতীয় বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০১০ সালে তাকে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য,
– “কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ” – এই উক্তিটি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন-এর। তিনি তার “Development as Freedom” গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন। এখানে ‘সামর্থ্যের অভাব’ বলতে শুধু আর্থিক সংগতিই নয়, বরং মানুষের সক্ষমতার অভাবকেও বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুযোগ এবং স্বাধীনতা লাভের অভাব।
এছাড়াও,
– অমর্ত্য সেনের লেখা গ্রন্থাবলি ৩০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
– The Idea Of Justice-গ্রন্থটির রচয়িতা অমর্ত্য সেন। বইটি মূলত জন রলসের ‘A Theory of Justice’ (1971)-এর মৌলিক ধারণাগুলির একটি সমালোচনা এবং সংশোধন।
উৎস: i) Britannica.
ii) Development as Freedom- Amartya Sen.
প্রশ্ন ৭৫. নিম্নোক্ত কোন রাষ্ট্রটি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য নয়?
ক) আজারবাইজান খ) ভারত
গ) পাকিস্তান ঘ) ইরান
সঠিক উত্তর: ক) আজারবাইজান
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ আজারবাইজান রাষ্ট্রটি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য নয়। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান ও ইরান সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য।
Shanghai Cooperation Organisation (SCO):
– সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) হলো একটি ইউরেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংস্থা।
– এর মূল লক্ষ্য আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
– গঠিত হয়: ১৫ জুন, ২০০১ সাল।
– সদরদপ্তর: বেইজিং, চীন।
– প্রতিষ্ঠিত সদস্য দেশ: ৬টি (চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান)।
– বর্তমান সদস্য দেশ: ১০টি (রাশিয়া, চীন, ভারত, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান, বেলারুশ)।
– সর্বশেষ সদস্য: বেলারুশ।
– বর্তমান মহাসচিব: Nurlan Yermekbayev।
– ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র: আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া।
উলেখ্য,
– ২০২৫ সালের Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-এর ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন চীনের তিয়ানজিন শহরে ৩১ আগস্ট -১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি SCO-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং।
উৎস: Shanghai Cooperation Organisation ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৭৬. ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি (IWT) কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ১৯৪৮ খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৬৫ ঘ) ১৯৮০
সঠিক উত্তর: “বাতিল করা হয়েছে”
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি (IWT) ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত হয়।
অপশনে সঠিক উত্তর না থাকায় প্রশ্নটি বাতিল করা হয়েছে।
সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি (Indus Waters Treaty):
– ভারতের উজান থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকায় প্রবাহিত নদীগুলোর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি হচ্ছে সিন্ধু পানি চুক্তি।
– চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সাল।
– চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান: করাচি, পাকিস্তান।
– মধ্যস্থতাকারী: বিশ্বব্যাংক।
– চুক্তি স্বাক্ষরকারী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান।
⇒ সিন্ধু পানি চুক্তি অনুসরণ করেই এসব নদীর পানি ব্যবহার করা হয়।
– এই চুক্তি সিন্ধু নদের অববাহিকার ছয়টি নদী দুই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।
– চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদীর নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। এগুলো হলো ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু।
– অন্যদিকে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদ–নদী অর্থাৎ সিন্ধু, ঝিলম এবং চেনাবের নিয়ন্ত্রণ। বলা হয় পশ্চিম অংশের এ তিনটি নদ–নদীর মাধ্যমে পাকিস্তানে মোট পানির প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ করে।
– চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান পায় ৭০ ভাগ পানি আর ভারত পায় ৩০ ভাগ পানি।
– চুক্তিটি কোনো দেশ একতরফাভাবে স্থগিত বা বাতিল করার বিধান নেই। বরং এতে সুস্পষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
অতিরিক্ত আলোচনা:
১৯৬০ সালে IWT স্বাক্ষরিত হলেও, ভারত ভাগের পর প্রথম আনুষ্ঠানিক জল-বণ্টন বন্দোবস্ত হয়েছিল ৪ মে ১৯৪৮—Inter-Dominion Agreement on Punjab Canal Waters. এই চুক্তিতে ভারত পাকিস্তানের অববাহিকায় পানি সরবরাহ দেবে, আর পাকিস্তান বার্ষিক অর্থপ্রদান করবে—যা ছিল স্থায়ী চুক্তি হওয়া পর্যন্ত একটি স্টপগ্যাপ/অন্তর্বর্তী সমাধান।
এই অন্তর্বর্তী বন্দোবস্তই পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক-মধ্যস্থ আলোচনার পথ খুলে দেয় এবং ১৯৬০ সালের IWT-তে পৌঁছাতে সহায়তা করে।
তাই প্রশ্নটি যদি “ইন্দাস ব্যবস্থায় দুই দেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক জল-ব্যবস্থাপনা চুক্তি/সমঝোতা”—এই অর্থে নেওয়া হয়, তহলে ক) ১৯৪৮ অধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর। কিন্তু প্রশ্নে সরাসরি এই চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে, এটা জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে ঘুরিয়ে উত্তর নেওয়ার সুযোগ কম।
উৎস:
i) Britannica.
ii) UNTC ওয়েবসাইট।
iii) Ministry of External Affairs, Government of India.
প্রশ্ন ৭৭. হালিমা ইয়াকুব কোন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
ক) ব্রুনেই খ) মালয়েশিয়া
গ) সিংগাপুর ঘ) তানজানিয়া
সঠিক উত্তর: গ) সিংগাপুর
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ হালিমা ইয়াকুব সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
হালিমা ইয়াকুব:
– হালিমা ইয়াকুব সিঙ্গাপুরের অষ্টম ও প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
– ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হালিমা ইয়াকুব ক্ষমতায় এসেছিলেন।
– ২০২৩ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ থারমান শানমুগারাতনাম হালিমা ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
উল্লেখ্য,
– সিঙ্গাপুরে প্রেসিডেন্ট পদ অনেকটা আলংকারিক। প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে নগররাষ্ট্রটির পুঞ্জীভূত আর্থিক রিজার্ভ দেখভাল করেন, সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এবং দুর্নীতিবিরোধী তদন্ত অনুমোদন করেন। তবে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বেশ কঠিন কিছু শর্ত রয়েছে। সংবিধান মতে, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে নির্দলীয় একটি পদ।
⇒ সিঙ্গাপুর:
– দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধনী নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুর।
– রাজধানী: সিঙ্গাপুর সিটি।
– মুদ্রা: সিঙ্গাপুরীয় ডলার।
– দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী: লরেন্স ওং (Lawrence Wong)।
– দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট: থারমান শানমুগারাতনাম (Mr Tharman Shanmugaratnam)।
– সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর স্ব-শাসিত হয়ে ওঠে।
এছাড়াও,
– আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক হলেন লি কুয়ান ইউ। লি কুয়ান ইউ ১৯৫৯ সালের জুন মাসে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
– তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে , সিঙ্গাপুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠে।
উৎস: Britannica.
প্রশ্ন ৭৮. সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ইসহাক দার পাকিস্তানের কোন্ রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত?
ক) পাকিস্তান পিপলস পাটি (PPP)
খ) পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (PTI)
গ) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ)
ঘ) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
সঠিক উত্তর: গ) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ)
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ইসহাক দার পাকিস্তানের পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) দলের সাথে সম্পৃক্ত।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার:
– মুহাম্মদ ইসহাক দার একজন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ।
– তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ২০২৪ সাল থেকে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
– ইসহাক দার পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) দলের সাথে সম্পৃক্ত।
– তিনি মুসলিম লীগ এন-এর প্রধান নওয়াজ শরীফের বেয়াই।
⇒ ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় অবতরণ করেন।
– ১৩ বছর পর বাংলাদেশ সফরে আসা পাকিস্তানের কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন ইসহাক দার। এর আগে ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তৎকালীন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রব্বানি ঢাকা সফর করেছিলেন।
উল্লেখ্য,
– পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের বাংলাদেশ সফরটি যতটা কূটনৈতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলেছেন। তাঁর সফরকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
উৎস: i) BBC.
ii) প্রথম আলো।
প্রশ্ন ৭৯. তুরস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল Kurdistan Workers’ Party বা PKK এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) জালাল তালাবানী খ) মাসুদ বারজানী
গ) মাজলুম আবদি ঘ) আবদুল্লাহ ওচালান
সঠিক উত্তর: ঘ) আবদুল্লাহ ওচালান
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ তুরস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল Kurdistan Workers’ Party বা PKK এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ওচালান।
Kurdistan Workers’ Party (PKK):
– কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) একটি কুর্দি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন।
– এটি মূলত তুরস্ক, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ায় কুর্দিদের অধিকারের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
– পিকেকে ১৯৭৮ সালে আবদুল্লাহ ওচালানের (Abdullah Ocalan) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
– পিকেকে শুরুতে একটি সাম্যবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
– সংগঠনটির মূল দাবি ছিল স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকেও মনোযোগ দেয়।
– পিকেকে-কে বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করলেও, অনেকের কাছে এটি কুর্দিদের অধিকারের জন্য সংগ্রামী প্রতিরোধ শক্তি।
উল্লেখ্য,
– পিকেকে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে।
– পিকেকে’র আদর্শ বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিগত-জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।
– ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো অন্যান্য দেশ সহ অনেক দেশ পিকেকেকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।
– পিকেকে’র প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু হল তুরস্কের পুলিশ, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদ।
– সম্প্রতি (১ মার্চ, ২০২৫) কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) দেশটির সরকারের সঙ্গে চলমান ৪০ বছরের সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে।
উৎস: i) BBC.
ii) Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs.
প্রশ্ন ৮০. প্রাচীনকালে কোন দেশে সিভিল সার্ভিসের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয়?
ক) মিশর খ) গ্রীস
গ) চীন ঘ) রোম
সঠিক উত্তর: গ) চীন
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
♦ প্রাচীনকালে সিভিল সার্ভিসের ধারণা প্রথম উদ্ভূত চীনে।
সিভিল সার্ভিস:
– সিভিল সার্ভিস একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা।
– এর মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান করে। এটি মূলত একটি পেশাদার, অরাজনৈতিক ও দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী বাহিনী, যারা সংবিধান ও সরকারের নীতিমালার আলোকে কাজ করে।
– এছাড়া, তারা সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের নানা স্তরে নিয়োজিত থাকেন।
⇒ সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হয়েছে – প্রাচীন কালেই; যখন কিনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।
– এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার তথ্য অনুসারে, সিভিল সার্ভিসের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক সভ্যতার সময়।
– পরবর্তীতে, রোমান সাম্রাজ্য প্রশাসনিক দপ্তর নির্মাণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল; যা পরবর্তীতে রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলোও অনুসরণ করে।
⇒ চীনে খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হয় যা চীনা সভ্যতা/সাম্রাজ্যকে দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে স্থায়িত্ব দিয়েছে।
– যোগ্যতার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসের প্রাচীনতম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হলো চীনের ইম্পেরিয়াল আমলাতন্ত্র।
– চীনে সিভিল সার্ভিসের চাকরিকে ‘Iron Rice Bowl’ বলা হয়। চাকরির নিরাপত্তা ও উচ্চ বেতনের জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে।
– চীনের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা মান্দারিন ভাষায় হয় ‘Guako’।
– খ্রিষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দে চীনের হান রাজবংশের রাজা গাওজু (Gaozu) এর শাসনামলে মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের উন্মেষ ঘটে। তিনি প্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করেন। এই সময়ে ইম্পেরিয়াল পরীক্ষা ব্যবস্থা (Keju বা Civil Service Examination) চালু হয়, যা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল। এই ব্যবস্থা পরবর্তীতে সুই (৫৮১-৬১৮) এবং তাং রাজবংশের (৬১৮-৯০৭) সময়ে আরও উন্নত হয়।
– পরবর্তীতে অন্যান্য রাজবংশের শাসনের সময় তা বিভিন্ন সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে ও অধিক সুসংগঠিত হয়।
– সং সাম্রাজ্য (Song Dynasty – 960–1279) প্রথম যোগ্যতা (jinshi degree) ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ঘটায়।
– মিং সাম্রাজ্যের (Ming dynasty – 1368–1644) সময় সিভিল সার্ভিস সিস্টেম চূড়ান্ত রূপে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে কিং সাম্রাজ্যও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। এই সময় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ নিজের এলাকায় নিয়োগ না পাওয়া, এক স্থানে তিনবছরের বেশি দায়িত্ব পালন না করা ইত্যাদি নিয়ম অন্তর্ভূক্ত হয়। তাছাড়া, উচ্চপদের জন্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জিনিস অন্তর্ভূক্ত এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়।
– চীনে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মূলত বর্তমান রাষ্ট্রীয় সিভিল সার্ভিসের প্রচলন ঘটে। সাধারণত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টরাই এই সার্ভিসে যোগদান করে।
• তাই, সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হিসেবে চীন দেশকেই গণ্য করা হয়।
উল্লেখ্য,
– ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর এই কাঠামো দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—ভারত ও পাকিস্তানের নিজ নিজ প্রশাসনিক কাঠামোতে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালে সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠিত হয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (BCS) নামে আত্মপ্রকাশ করে।
উৎস: i) Britannica.
ii) BBC.
গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা
প্রশ্ন ৮১. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 48 বর্গমিটার। ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?
ক) 2√2 মিটার খ) 2√3 মিটার
গ) 2 মিটার ঘ) 2√6 মিটার
সঠিক উত্তর: ঘ) 2√6 মিটার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 48 বর্গমিটার
আমরা জানি,
ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = 6a2, [যেখানে a হলো ঘনকের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য।]
প্রশনমতে,
6a2 = 48
⇒ a2 = 48/6
⇒ a2 = 8
⇒ a = √8 = 2√2
∴ a = 2√2 মিটার
আবার,
আমরা জানি,
ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য = a√3
= (2√2) × √3 ; [a = 2√2]
= 2√(2 × 3)
= 2√6
সুতরাং, ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য 2√6 মিটার।
প্রশ্ন ৮২. একটা লোহার গোলক গলিয়ে কয়টি সমান আয়তনের গোলক তৈরী সম্ভব যাদের প্রত্যেকের ব্যাসার্ধ বড় গোলকটির অর্ধেক?
ক) ৪ খ) ৮ গ) ১৬ ঘ) ২
সঠিক উত্তর: খ) ৮
Live MCQ Analytics™: Right: 19%; Wrong: 13%; Unanswered: 67%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
ধরি,
বড় গোলকের ব্যাসার্ধ = R
ছোট গোলকের ব্যাসার্ধ, r = R/2
আমরা জানি,
গোলকের আয়তন V = (4/3)πr3
এখন,
বড় গোলকের আয়তন = (4/3)πR3
ছোট গোলকের আয়তন = (4/3)π(R/2)3 = (1/8) × (4/3)πR3
∴ ছোট গোলকের সংখ্যা = বড় গোলকের আয়তন ÷ ছোট গোলকের আয়তন
= {(4/3)πR3} ÷ {(1/8) × (4/3)πR3}
= 1/(1/8)
= 8
সুতরাং, বড় গোলকটি গলিয়ে ৮টি সমান ছোট গোলক তৈরি করা সম্ভব।
প্রশ্ন ৮৩. logx4 = – 2 হলে x = কত?
ক) 1/2 খ) – 1/2
গ) 2 ঘ) – 2
সঠিক উত্তর: ক) 1/2
Live MCQ Analytics™: Right: 45%; Wrong: 20%; Unanswered: 33%; [Total: 18630]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
logx4 = – 2
⇒ 4 = x– 2
⇒ 4 = 1/x2
⇒ x2 = 1/4
⇒ x2 = (1/2)2
∴ x = 1/2
প্রশ্ন ৮৪. একটি ত্রিভুজের প্রথম কোণ দ্বিতীয় কোণের অর্ধেক। তৃতীয় কোণ অপর দুই কোণের বিয়োগফলের তিনগুণ। দ্বিতীয় কোণটি কত ডিগ্রী?
ক) ৩০ খ) ৬০ গ) ৯০ ঘ) ৪৫
সঠিক উত্তর: খ) ৬০
Live MCQ Analytics™: Right: 50%; Wrong: 10%; Unanswered: 38%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
ধরি,
দ্বিতীয় কোণ = x
প্রথম কোণ দ্বিতীয় কোণের অর্ধেক।
∴ প্রথম কোণ = x/2
এবং,
তৃতীয় কোণটি অপর দুই কোণের বিয়োগফলের তিনগুণ।
অর্থাৎ, তৃতীয় কোণ = 3{x – (x/2)} = 3(2x – x)/2 = 3x/2
আমরা জানি,
ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সর্বদা 180°
প্রশ্নমতে,
x + (x/2) + (3x/2) = 180°
⇒ (2x + x + 3x)/2 = 180°
⇒ 6x/2 = 180°
⇒ 3x = 180°
⇒ x = 180°/3
∴ x = 60°
অতএব, দ্বিতীয় কোণটি হলো 60°.
প্রশ্ন ৮৫. একটি সমান্তর ধারার 4র্থ (চতুর্থ) এবং 12 তম পদের যোগফল 20 । ঐ ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল কত?
ক) 100 খ) 150 গ) 200 ঘ) 300
সঠিক উত্তর: খ) 150
Live MCQ Analytics™: Right: 28%; Wrong: 2%; Unanswered: 68%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
আমরা জানি,
সমান্তর ধারার n-তম পদ = a + (n – 1)d ; যেখানে a = প্রথম পদ, d = সাধারণ অন্তর।
সুতরাং,
সমান্তর ধারার 4র্থ পদ = a + (4 – 1)d = a + 3d
সমান্তর ধারার 12 পদ = a + (12 – 1)d = a + 11d
প্রশ্নমতে,
a + 3d + a + 11d = 20
∴ 2a + 14d = 20 …….. (1)
আবার,
সমান্তর ধারার প্রথম n পদের যোগফল = (n/2) × {2a + (n – 1)d}
∴ সমান্তর ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল = (15/2) × {2a + (15 – 1)d}
= (15/2) × {2a + 14d}
= (15/2) × 20 ; [(1) নং হতে]
= 15 × 10
= 150
সুতরাং, ঐ ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল 150
প্রশ্ন ৮৬. x2 + 6x – 27 < 0 অসমতাটির সমাধান সেট নিচের কোনটি?
ক) [-9, 3] খ) [3, ∞)
গ) (-9, 3) ঘ) (∞, -9)
সঠিক উত্তর: গ) (-9, 3)
Live MCQ Analytics™: Right: 37%; Wrong: 20%; Unanswered: 41%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
⇒ x2 + 6x – 27 < 0
এখন,
⇒ x2 + 9x – 3x – 27 = 0
⇒ x(x + 9) – 3(x + 9) = 0
⇒ (x + 9)(x – 3) = 0
হয়, (x + 9) = 0
∴ x = – 9
এবং, (x – 3) = 0
∴ x = 3
অসমতাটি হলো x2 + 6x – 27 < 0 যেহেতু এটি একটি দ্বিঘাত অসমতা, এর সমাধানটি মূল দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হবে। অর্থাৎ, x এর মান – 9 এবং 3 এর মধ্যে থাকবে।
সুতরাং, সমাধান সেট = (- 9, 3)
বিকল্প সমাধান:
যদি x = – 10 হয়, তাহলে (- 10)2 + 6(- 10) – 27 = 100 – 60 – 27 = 13 > 0
যদি x = 0 হয়, তাহলে (0)2 + 6(0) – 27 = 0 – 0 – 27 = – 27 < 0
যদি x = 4 হয়, তাহলে (4)2 + 6(4) – 27 = 16 + 24 – 27 = 13 > 0
সুতরাং, সমাধান সেটটি (-9, 3) এর মধ্যে অবস্থিত।
প্রশ্ন ৮৭. একটা বাক্সে ৪টা লাল, ৩টা নীল, ২টা হলুদ ও ১টা সবুজ বল আছে। কমপক্ষে কয়টা বল উঠালে সেখানে অন্তত একটা লাল বল থাকবেই?
ক) ৫ খ) ৬ গ) ৭ ঘ) ৮
সঠিক উত্তর: গ) ৭
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
লাল বল = ৪
নীল বল = ৩
হলুদ বল = ২
সবুজ বল = ১
মোট = ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০ বল
সমাধান করতে হবে: কমপক্ষে কয়টা বল তুললে অন্তত একটি লাল বল উঠবেই।
– কমপক্ষে লাল বল বের করার জন্য worst case বিবেচনা করতে হবে।
worst case = প্রথমে সব লাল না তুলে বাকি সব রঙের বল তুলতে হবে।
লাল নয় এমন বলের সংখ্যা = ৩ + ২ + ১ = ৬
অতএব, ৬টা বল তোলার পরও আমরা কোনো লাল বল নাও পেতে পারি।
এখন,
৬টা লাল নয় এমন বলের পর আরও ১টা বল তুললে লাল বল আসবেই।
অতএব, ৭টা বল তুলতে হবে।
সঠিক উত্তর: (গ) ৭
প্রশ্ন ৮৮. যদি M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2} হয়, তবে N – M এর মান কত?
ক) { } খ) {a, b}
গ) { 0 } ঘ) {- a, – b}
সঠিক উত্তর: ক) { }
Live MCQ Analytics™: Right: 46%; Wrong: 26%; Unanswered: 27%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2}
প্রদত্ত রাশি,
N – M = {1, 2} – {a, b, 1, 2} = { }
N – M = { }
অথবা,
যদি M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2} হয়, তবে N – M এর মান হলো একটি খালি সেট, অর্থাৎ ∅ বা { }। এর কারণ হলো N সেটের সকল উপাদান (1 এবং 2) M সেটে উপস্থিত রয়েছে। N – M মানে হলো N সেটের এমন সকল উপাদান যা M সেটে নেই, এবং এই ক্ষেত্রে এমন কোনো উপাদান নেই।
সুতরাং, N – M = ∅ বা {}
প্রশ্ন ৮৯. ax + by = a2; bx – ay = ab; এই সহ-সমীকরণের (x, y) এর সমাধান কোনটি?
ক) (a2, b2) খ) (a, b)
গ) (0, a) ঘ) (a, 0)
সঠিক উত্তর: ঘ) (a, 0)
Live MCQ Analytics™: Right: 32%; Wrong: 5%; Unanswered: 62%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
ax + by = a2 ………… (1)
bx – ay = ab……….(2)
সমীকরণ (1)-কে b দিয়ে গুণ করে পাই, abx + b2y = a2b…….(3)
সমীকরণ (2)-কে a দিয়ে গুণ করে পাই, abx – a2y = a2b…….(4)
এখন, (3) – (4) করে পাই,
abx + b2y – abx + a2y = a2b – a2b
⇒ y(a2 + b2) = 0
∴ y = 0
y এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই,
ax + 0 = a2
⇒ x = a2/a = a
∴ x = a
সুতরাং, সমাধান (x, y) = (a, 0)
প্রশ্ন ৯০. একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদটি ৩২ ও অষ্টম পদটি ২৫৬ হলে উক্ত ধারার সাধারণ অনুপাত কত?
ক) ৮ খ) ১৬ গ) ২ ঘ) ১/২
সঠিক উত্তর: গ) ২
Live MCQ Analytics™: Right: 49%; Wrong: 5%; Unanswered: 44%; [Total: 18630]
ব্যাখ্যা:
আমরা জানি,
একটি গুণোত্তর ধারার n-তম পদ = arn -1
দেওয়া আছে,
৫ম পদ, ar4 = 32 ………(১)
৮ম পদ, ar7 = 256 ………(২)
এখন, (২) নং কে (১) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,
ar7/ar4 = 256/32
⇒ r3 = 8
⇒ r3 = 23
∴ r = 2
সুতরাং, ধারাটির সাধারণ অনুপাত ২ ।
প্রশ্ন ৯১. একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে ১০০ ফুট বেগে চলছে। এক ব্যক্তির বন্দুকের গুলির বেগ সেকেন্ডে ২০০ ফুট। উক্ত ব্যক্তি চলন্ত ট্রেনের ৩০০ ফুট সামনে একটা স্তম্ভ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কত সেকেন্ড পর তা স্তম্ভকে আঘাত করবে?
ক) ৩ খ) ১.৫ গ) ১ ঘ) ০.৫
সঠিক উত্তর: গ) ১
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
ট্রেনের বেগ = ১০০ ফুট/সেকেন্ড
গুলির বেগ = ২০০ ফুট/সেকেন্ড
স্তম্ভের দূরত্ব = ৩০০ ফুট
ব্যক্তি ট্রেনের উপর থেকে সামনের দিকে গুলি ছুড়েছে, তাই গুলির আপেক্ষিক কার্যকর বেগ = ট্রেনের বেগ + গুলির বেগ।
কার্যকর বেগ = ২০০ + ১০০ = ৩০০ ফুট/সেকেন্ড
সময় = দূরত্ব ÷ বেগ = ৩০০ ÷ ৩০০ = ১ সেকেন্ড
প্রশ্ন ৯২. দুইটি সংখ্যার ল,সা, গু 4x2 + 12x2 – 16x – 48, গ,সা,গু 2x+4। একটি সংখ্যা 4x2 + 20x + 24 হলে অপরটি-
ক) x2 – 4 খ) 2(x2 – 4)
গ) 4(x2 – 4) ঘ) x + 2
সঠিক উত্তর: খ) 2(x2 – 4)
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
প্রশ্ন: দুইটি সংখ্যার ল,সা, গু 4x2 + 12x2 – 16x – 48, গ,সা,গু 2x+4। একটি সংখ্যা 4x2 + 20x + 24 হলে অপরটি-
সমাধান:
[মূল প্রশ্নে 4x2 + 12x2 – 16x – 48 অংশটি ভুল দেওয়া আছে, এটি: 4x3 + 12x2 – 16x – 48 হবে, তাই ল,সা, গু 4x3 + 12x2 – 16x – 48 ধরে সমাধান করা হয়েছে]
ল,সা, গু = 4x3 + 12x2 – 16x – 48
গ,সা,গু = 2x + 4
একটি সংখ্যা = 4x2 + 20x + 24
অপর সংখ্যা = ?
আমরা জানি,
প্রথম সংখ্যা × দ্বিতীয় সংখ্যা = ল.সা.গু × গ.সা.গু
গ,সা,গু = 2x + 4 = 2(x + 2)
একটি সংখ্যা = 4x2 + 20x + 24
= 4(x2 + 5x + 6)
= 4(x + 2)(x + 3)
ল,সা, গু = 4x3 + 12x2 – 16x – 48
= 4(x3 + 3x2 – 4x – 12)
= 4[x2(x + 3) – 4(x + 3)]
= 4(x + 3)(x2 – 4)
= 4(x + 3)(x – 2)(x + 2)
প্রথম সংখ্যা × দ্বিতীয় সংখ্যা = ল.সা.গু × গ.সা.গু
দ্বিতীয় সংখ্যা = [4(x + 3)(x – 2)(x + 2) × 2(x + 2)] / [4(x + 2)(x + 3)]
= [8(x + 3)(x – 2)(x + 2)2] / [4(x + 2)(x + 3)]
= 2(x – 2)(x + 2)
= 2(x2 – 4)
প্রশ্ন ৯৩. যদি গতকাল শুক্রবার হতো, তাহলে আজ থেকে ৮১ তম দিন কি বার হবে?
ক) শুক্রবার খ) বুধবার
গ) সোমবার ঘ) রবিবার
সঠিক উত্তর: খ) বুধবার
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
গতকাল শুক্রবার ছিল।
অতএব, আজ শনিবার।
এখন আজ থেকে ৮১ তম দিন কোন বার হবে তা বের করতে হবে।
প্রতি সপ্তাহে ৭ দিন থাকে, তাই আমরা ৮১ কে ৭ দিয়ে ভাগ করব:
৮১ ÷ ৭ = ১১ সপ্তাহ এবং ৪ দিন।
অতএব, ৮১ দিনের ব্যবধান মানে ৪ দিন পরের বার।
এখন আজ (শনিবার) থেকে ৪ দিন যোগ করি:
আজ = শনিবার (দিন ০)
দিন ১ = রবিবার
দিন ২ = সোমবার
দিন ৩ = মঙ্গলবার
দিন ৪ = বুধবার
∴ সঠিক উত্তর: বুধবার
প্রশ্ন ৯৪. নীচের ধারার পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? ১, √৯, ৫, √৪৯, ……
ক) ৮ খ) ৯ গ) ১০ ঘ) ১২
সঠিক উত্তর: খ) ৯
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
দেওয়া ধারা: ১, √৯, ৫, √৪৯, ……
প্রথম পদ = ১
দ্বিতীয় পদ = √৯ = ৩
তৃতীয় পদ = ৫
চতুর্থ পদ = √৪৯ = ৭
পঞ্চম পদ = ?
এখন সংখ্যাগুলি দেখি: ১, ৩, ৫, ৭…….
প্যাটার্ন: এটি একটি বিজোড় সংখ্যার ধারা যেখানে প্রতিটি পদ আগের পদ থেকে ২ বেশি।
১ থেকে ৩ = +২
৩ থেকে ৫ = +২
৫ থেকে ৭ = +২
৭ থেকে ? = +২
পরবর্তী সংখ্যা = ৭ + ২ = ৯
∴ সঠিক উত্তর: খ) ৯
প্রশ্ন ৯৫. ১ জন লোক ১ টা কলা ১ মিনিটে খেতে পারে। তাহলে ৫ জন লোকের ৫ টা কলা খেতে কত মিনিট সময় লাগবে?
ক) ৫ খ) ২৫ গ) ১ ঘ) ১০
সঠিক উত্তর: গ) ১
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
১ জন লোক ১ টা কলা = ১ মিনিট
১ জন লোক ৫ টা কলা = ৫ মিনিট
৫ জন লোক ১ টা করে কলা = ১ মিনিট (সবাই একসাথে খায়)
৫ জন লোক ৫ টা কলা = ১ মিনিট (প্রতিটি লোক ১ টা কলা খায়)
কারণ: যখন ৫ জন লোক একসাথে খায়, তারা একই সময়ে কলা খাওয়া শুরু করে এবং শেষ করে। প্রতিটি লোক ১ টা কলা খেতে ১ মিনিট সময় নেয়।
প্রশ্ন ৯৬. একটি বই 10% ক্ষতিতে বিক্রি করা হইল। বিক্রয়মূল্য 60 টাকা বেশী হলে 5% লাভ হত। বইটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?
ক) 200 খ) 300 গ) 400 ঘ) 500
সঠিক উত্তর: গ) 400
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
ধরি,
বইটির ক্রয়মূল্য = 100 টাকা
10% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য = 100 – 10 = 90 টাকা
5% লাভে, বিক্রয়মূল্য = 100 + 5 = 105 টাকা
∴ বিক্রয়মূল্য বেশি = 105 – 90 = 15 টাকা
বিক্রয়মূল্য 15 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = 100 টাকা
বিক্রয়মূল্য 1 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = 100/15 টাকা
বিক্রয়মূল্য 60 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = (100 × 60)/15 টাকা
= 400 টাকা
সুতরাং, বইটির ক্রয়মূল্য 400 টাকা।
প্রশ্ন ৯৭. কোন যান্ত্রিক গিয়ারের চাকা ছোট হলে সংযুক্ত অবস্থায় বড়টির চেয়ে ছোট চাকাটি কিভাবে ঘুরবে?
ক) আস্তে খ) জোরে
গ) একইভাবে ঘ) কোনটিই নয়
সঠিক উত্তর: খ) জোরে
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
গিয়ার মেকানিজমের নীতি:
যখন দুটি গিয়ার চাকা সংযুক্ত থাকে, তখা তারা একে অপরকে স্পর্শ করে এবং চলে।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
– ছোট চাকার দাঁতের সংখ্যা < বড় চাকার দাঁতের সংখ্যা
– যখন সংযুক্ত থাকে, উভয় চাকার দাঁত একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই সংখ্যক বার মিলিত হয়
গতির সম্পর্ক:
– ছোট চাকাটি বড় চাকার চেয়ে দ্রুত গতিতে ঘোরে (জোরে/বেগে ঘোরে)।
কারণ:
– যদি বড় চাকায় 100 দাঁত এবং ছোটটায় 20 দাঁত থাকে
– বড় চাকা 1 বার ঘুরলে, ছোট চাকা 5 বার ঘোরে
– তাই ছোট চাকা আরও বেশি দ্রুত ঘোরে
– সঠিক উত্তর: খ) জোরে
সুতরাং, ছোট চাকাটি বড় চাকার চেয়ে জোরে/দ্রুত গতিতে ঘোরে।
প্রশ্ন ৯৮. ১৫ মিটার লম্বা একটি স্কেলের এক প্রান্তে ১০ কেজি ওজন বাঁধা হয়েছে। একই প্রান্ত থেকে স্কেলের দৈর্ঘ্যের ৩ : ২ অনুপাতে একটি পেরেক লাগানো আছে। অপর প্রান্তে কত কেজি ওজন দিলে স্কেলের ভারসাম্য থাকবে?
ক) ৪৫ খ) ৩০ গ) ১৫ ঘ) ৫
সঠিক উত্তর: গ) ১৫
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
স্কেলের মোট দৈর্ঘ্য = ১৫ মিটার
এক প্রান্তের ওজন = ১০ কেজি
পেরেক বিভাজন = ৩ : ২
৩ : ২ অনুপাতে পুরো ১৫ মিটারকে ৫ ভাগে ভাগ করলে পেরেকটি এক প্রান্ত থেকে ৯ মিটারে আছে। অপর অংশ = ৬ মিটার। ভারসাম্য শর্ত অনুযায়ী টর্ক সমান হবে।
বাঁ দিকের টর্ক = ১০ কেজি × ৯ মিটার = ৯০
ডান দিকের টর্ক = W × ৬ মিটার
W = ৯০ ÷ ৬ = ১৫ কেজি
সঠিক উত্তর: গ) ১৫ কেজি
প্রশ্ন ৯৯. একটি থলিতে 3 টি সবুজ এবং 2 টি লাল বল আছে। অপর একটি থলিতে 2 টি সবুজ এবং 5 টি লাল বল আছে। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক থলি থেকে একটি করে বল তোলা হল। দুইটি বলের মধ্যে অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?
ক) 5/7 খ) 2/7
গ) 5/12 ঘ) 1/4
সঠিক উত্তর: ক) 5/7
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা:
প্রথম থলিতে, 3 টি সবুজ বল, 2 টি লাল বল
দ্বিতীয় থলিতে, 2 টি সবুজ বল, 5 টি লাল বল
অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা = 1 – দুইটি বলই লাল
প্রথম থলি থেকে লাল বলের সম্ভাবনা = 2/5
দ্বিতীয় থলি থেকে লাল বলের সম্ভাবনা = 5/7
দুইটি লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা = (2/5) × (5/7) = 2/7
অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা = 1 – (2/7) = 5/7
∴ সঠিক উত্তর: ক) 5/7
প্রশ্ন ১০০. PQR ত্রিভূজের ∠Q =90° এবং ∠P = 2∠R হলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক) PR = 2QR খ) PQ = 2PR
গ) PR = 2PQ ঘ) QR = 2PQ
সঠিক উত্তর: গ) PR = 2PQ
Live MCQ Analytics™: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
এখানে,
∠Q = 90°
∠P = 2∠R
আমরা জানি,
∠P + ∠Q + ∠R = 180°
∠Q = 90°
⇒ ∠P + ∠R = 90°
∠P = 2∠R
⇒ 2∠R + ∠R = 90°
⇒ ∠R = 30°,
∴ ∠P = 60°
সমকোণ ত্রিভুজে,
PR = অতিভুজ
QR = বিপরীত ∠P,
PQ = বিপরীত ∠R
sin P = QR / PR
→ sin 60° = √3/2
→ QR = (√3/2) PR
sin R = PQ/PR
→ sin 30° = 1/2
→ PQ = (1/2) PR
সুতরাং, PR = 2 PQ
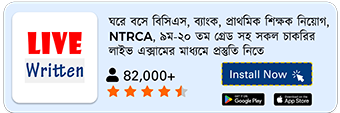
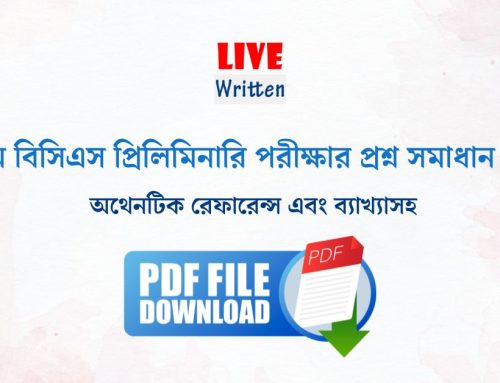

Leave A Comment